কলাভবনের চিত্রী মাস্টারমশাই সুখময় মিত্রকে বৃদ্ধ বয়সে দেখে এবং তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে ছিটগ্রস্ত, আজগুবি বা উৎকট – এসব কিছুই মনে হয়নি। শুধু মনে হয়েছিল যে, তিনি যেন লীলা মজুমদারের লেখা এক জীবন্ত চরিত্র। কথার ফাঁকে ফাঁকে ছোট্ট একটি হাতটানা বন্দুকে, কাগজের পাকানো গুল্লি একটা একটা করে ভরে, থেকে থেকেই নিজের ঘরের ভেতর থেকে শুনশান উঠোনের দিকে তাক করছেন আর বলছেন, ‘তবে রে?’ বুঝলাম যে, অদৃশ্য হনুমানদের উদ্দেশ্যে। তাঁর আজগুবি ভাবনার এক নিরেট হদিশ মিলল, যখন উনি নিজের লেখা এবং নিজের পয়সায় ছাপানো কয়েকটি বই, স্বাক্ষর করে আমাকে উপহার দিলেন। তার মধ্যে একটি হল “পা.হি.বা” – নতুন একটি রাষ্ট্র হতে চলেছে – পাকিস্তান, হিন্দুস্তান এবং বাংলাদেশ মিলিয়ে। তার মানচিত্রটি দেখিয়ে বললেন, বোলপুর থেকে দিল্লি হয়ে, কী ভাবে তিনি বাংলাদেশ সীমান্ত পার হয়ে, ব্রহ্মদেশটাও সংযুক্ত করবেন। “পা.হি.বা” হাতে পেয়ে চট করে কেন যে মনে এসেছিল ‘পেরিস্তান’, কে জানে! স্বপ্নও কি আসলে এক আজগুবি আয়েশ? লীলা মজুমদার লিখেছেন না, “মানব হৃদয়ের সব অনুভূতির জায়গা আছে আজগুবিতে।”
লীলা মজুমদার আমার জীবনে নানা ভাবে, বারে বারে এসেছেন। আর বেশির ভাগ সময়তেই খুব সরাসরি। ক্লাস ফোরের কোনও এক গরমের ছুটিতে, দুপুরবেলা মায়ের দু’পাশে দু’বোনে শুয়ে শুনতে লাগলাম, ‘পদিপিসির বর্মিবাক্স।’ হঠাৎ করে অবনীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায় ছেড়ে ইনি কে? মা পড়ছেন আর ‘তকাই’ এর মতো গড়াগড়ি খেয়ে হাসছেন। আমি প্রায় কিছুই বুঝলাম না, বোন ঘুমিয়ে পড়ল। মাঝখান থেকে মায়ের পাশ ছেড়ে টুক করে উঠে পড়ে, ছাদে গিয়ে বন্ধু মানাকে একটু আগে থাকতেই খেলতে আসার জন্য ডাকাডাকি করতে লাগলাম।
কিন্তু, এরপর থেকেই উপহারে এবং প্রাইজে পেতে লাগলাম তাঁর বই। সে সব বই তখন খুব যে কিছু পড়েছি, তা মনে নেই। তবে লীলা মজুমদার নামটি বাড়িতেই বড়দের নানা আলোচনায় স্থান পেত। এখন বুঝি যে সে সময় প্রবাসী এবং কলকাতাবাসী শিক্ষিত বাঙালি মেয়েদের এক ধরণের চেনাচেনি চলত। আর তা সহজ হত এই কারণে যে, এঁদের বাবারা বেশিরভাগই উচ্চপদস্থ সরকারি চাকুরে। কিছুটা সাহেবিয়ানা, কিছুটা ব্রাহ্ম প্রভাব, স্বদেশীয়ানা এবং সংস্কারমুক্ত মন, এই সব মেয়েদের যৌথতা দিত। গণ্ডিই বা কতটুকু! ঘুরে ফিরে ওই তো ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়, আশুতোষ কলেজ, বেতার, নাগালের পত্র পত্রিকা আর অসংখ্য সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান; আর যাতায়াতের মধ্যে এদিকে গিরিডি, মধুপুর, হাজারিবাগ, পটনা, কটক বা ওদিকে আসাম, শিলং বা বড়জোর বার্মা। আর কেউ কেউ দিল্লি, শিমলে পার করে বিলেত, মিশর, আফ্রিকা। আর প্রায় সকলেই কোনও না কোনও ভাবে অল্পদিন হলেও শান্তিনিকেতন।
আমাদের বাড়ির সূত্রেও, বাপ-ঠাকুরদার কল্যাণে যেহেতু মা-পিসিমাদের ঘোরাঘুরি এবং শিক্ষা সূত্রগুলিও প্রায় এক, তাই তাঁর নাম আলোচিত হলে মনে হত, আমিও যেন তাঁকে অনেক কাল ধরেই চিনি। তাঁর মেধা, কর্মশক্তি এবং কলমের অন্ধ ভক্ত ছিলেন আমাদের পিসিমারা এবং বিশেষ করে মা, কারণ আমৃত্যু তাঁর দুর্বলতা ছিল ইংরেজিতে লেখা বিদেশি সাহিত্য আর ইংরেজি নিয়ে উচ্চশিক্ষা।
আমি লীলা মজুমদারকে আবিষ্কার করলাম, ‘আর কোনোখানে’ বইটি পড়ে। ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ শেষ হল না, মন ঘুরে বেড়াতে লাগল শিলং পাহাড়ের এক অপরিচিত বালিকার পায়ে পায়ে, ঠিক যেন আমার খড়দা ছেড়ে কলকাতায় আসার একরাশ মনখারাপে, আলুর ঝালুর গপ্পো। এরপর তো কলেজ। ‘স্বপন বুড়ো’, ‘মৌমাছি’, ‘জীবন সর্দার’ ছাপিয়ে, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর। আর গোগ্রাসে নভেল গেলার সময়ে এসে গেল, ইংরেজি বইগুলোও। তখন বুঝলাম, কিশোরী বেলায় যা কিছু নভেল বাংলা অনুবাদে পড়েছি, তার মধ্যে কয়েকটির অনুবাদকও এই লীলা মজুমদার। তাঁকে একবারই চাক্ষুষ দেখেছি, বিধান শিশু উদ্যানে। সাদা শাড়িপরা, খোঁপা বাঁধা একজন বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ। অতুল্য ঘোষের সঙ্গে অনেক গল্প করলেন। সেদিনের সভাতেও সুন্দর করে কিছু কথা বলে গেলেন। আমাদের নীরেনদা, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী খুব সুন্দর করে তাঁর একটা পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। অতুল্য ঘোষ পরে বলেছিলেন, ইংরেজিতে বাংলা লেখে তো, তাই ওর লেখা এত মেদহীন। কিন্তু তখন একটা খটকাও লেগেছিল। যে মানুষটি আমাকে রাণী চন্দের সবকটি বই উপহারে দিয়েছেন, তিনি কেন লীলা মজুমদার দেননি! মাঝের পর্বে আর তিনি আমার লেখক তালিকায় নেই। অন্য লেখকদের সঙ্গে বুঁদ হয়ে পড়ি মহাশ্বেতা দেবী আর কবিতা।
আবার তাঁকে খেয়াল পড়ল তাঁর শতবর্ষে। জীবিত মানুষের শতবর্ষ পালন টিভিতে দেখে, আমার অসুস্থ এবং চৈতন্যহীন মায়ের আয়াটি সমানেই বলতে লাগল, আমাদের এই মা-ও তো তাহলে একশো বছর বাঁচবেনই, ফলে তার ছেলের মাধ্যমিক দেওয়াটাও এ বাড়ি থেকেই হয়ে যাবে। তখন মনে এল যে, আমার মা, যিনি রান্নাবান্না ও ‘বাড়ি বাড়ি খেলা’র থেকেও কমিটি, ট্রাস্টি, মেম্বার, মিটিং, কোরাম এবং এজেন্ডাকেই প্রাণের আরাম বলে মনে করতেন, তিনিও লীলা মজুমদারের রান্নার বই পড়ে হেসে গড়িয়ে, দু’এক পদ রেঁধে খাইয়ে ছিলেন। বিশেষত ‘আমোদিনীর নুড়নুড়ি ডাল।’
সেই শতবর্ষের জোয়ারে এবং এর অল্প পরেই তাঁর প্রয়াণের পর, সুযোগ হল তেড়ে ধরে তাঁকে পড়ে ফেলার। মনে হল না যে পড়িনি, মনে হল না যে, বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে। ২০০০ সালের গোড়ায় উত্তর ছেড়ে, দক্ষিণ কলকাতায় থাকার সূত্রে এবং শান্তিনিকেতনে এক নিবিড় বন্ধু গোষ্ঠী পাওয়ায়, এই নতুন পরিচিতদের এর ওর গল্পে, উনি এলেন কখনও বালিগঞ্জ পার্কের লীলা দিদু, কখনও লীলা পিসি, কখনও লীলা মাসিমা, কখনও বা লীলা দিদি হয়ে, শুধু লেখায় নয়, আত্মজনের ছবিতেও। তখন ওঁর জীবন একরকম সম্পূর্ণ এবং স্তব্ধ। বছর তিনেক আগে, শিলং হয়ে মেঘালয় বেড়াতে গিয়ে ‘শেষের কবিতার’ সঙ্গে সঙ্গে মনে ভাসছিল, তাঁর শিলং বাস আর ছোট্ট সেই ‘বড়াপানি’ বইটির কথা। আমরাও যেন ওঁদের বাড়ির অতিথি হয়েই পাহাড়বাসে এসেছি। খাসিয়া মেয়ে ‘কাকমা উবিন’ও আশে পাশেই কোথাও আছে। এখানেই যেন সেই দাদা–দিদি-কল্যাণ আর যতি।

মন ভরে তাই অপলক চেয়েছিলাম, ‘পাকদণ্ডী’ আস্তে আস্তে, ঘুরে ঘুরে, ছায়ায় ছায়ায় উঠত। মাঝে মাঝে মনে হত বুঝি বনের মধ্যে ঢুকল। দু’দিকের গাছ ঝুঁকে পড়ে পথটাকে কোলে নিত। আর এই গত বছরেই কলেজের রবীন্দ্র-দিবস উপলক্ষে মে মাসে কিছু বই কেনার তালিকা করতে গিয়ে দেখি, তাঁর লেখা একটি বই ‘এই যা দেখা’ – রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষে লেখা, বিশ্বভারতী প্রকাশনা। কিন্তু ছাপা নেই। কলেজ লাইব্রেরিতে গিয়ে প্রথম প্রকাশ, প্রথম সংস্করণ পেয়ে, এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম। কবি বলে উল্লেখ করলেও একবারও লেখেননি গুরুদেব, অথচ এমন ভালবেসে অথচ যুক্তিতে রবীন্দ্রনাথকে দেখা! আবার অভিমানে মনে হল, অতুল্য ঘোষ কেন এমন একখানি বইয়ের সূত্র আমাকে জানাননি। আর এও দেখলাম যে নানা জনের নানা কথা, এমনকি অনিল চন্দ থাকলেও, কোথাও রাণী চন্দ নেই। রবীন্দ্রায়ণের ভিন্ন সরণিতে যে লীলা মজুমদার, সে কথার একটা সূত্র পেলাম। পরে জানছি, অন্যত্র ব্যক্তিগত স্মৃতি চারণায় যা লিখেছেন, সে কথাই বা কোথায় কে কবে লিখেছেন! “রবীন্দ্রনাথ একদিন পাকা ধানের ক্ষেতের ধারে আমাকে দাঁড় করিয়ে ধানের গান শোনালেন। বাতাসের দোলা লেগে পাকা ধানের শীষ একটার পর আরেকটা আছড়ে পড়ছে আর মধুর এক ঝম-ঝম-ঝম শব্দ উঠছে।” শান্তিনিকেতন সম্পর্কে লিখেছেন, “মনে হত একটা নিশ্বাসের শব্দও এখানে নষ্ট হয় না।” ফলে, পরিণত বয়সে ক্রমেই নাগালে পেলাম, তাঁর গভীর যাপন ও বোধ যার বীজ তিনি অনায়াসে বুনে গেছেন তাঁর নানা খুনসুটির আড়ালে। ‘পাকদণ্ডী’তে, যেমন তাঁর মুকুলদা সম্পর্কে লিখেছেন, “আমি ওকে কখনও কিছু দিইনি। দেওয়া যায়না।” তীব্র দুঃখ প্রসঙ্গে লিখেছেন, “কষ্ট হলে কাঁদতে পারিনা আমি। অন্তরের অন্তঃস্থলে কোথায় একটা ঘট রাখা আছে, সব চোখের জল সেইখানে জমা হয়।” কত রকম ভাবে যে নিজেকে দেখেছেন, গড়েছেন আর ভেঙেছেন। কিন্তু সব অবস্থানেই চেয়েছেন শুধু লিখে যেতে।
এই যে অনড় এক আস্থা, লেখা ছাড়া তাঁকে দিয়ে আর যে কিছুই হবেনা, এও খুব বিস্ময়কর। গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের “Living to Tell The Tales” বইটি পড়ছিলাম। এরই মধ্যে হাতে এল ‘পাকদণ্ডী।’ অগত্যা সময় ভাগাভাগি করে প্রায় দু’টো বইই একসঙ্গে চলছে। দু’জনেই তর হয়ে ডুবে আছেন কিশোর বেলার জাদুবাস্তবে। দু’জনেই বলছেন, আশপাশের শোনা কথাগুলোও যেন নিজের দেখা। ‘ What matters in life is not what happens to you, but what you remember and how you remember it।’ লীলা লিখছেন, “সারা জীবন বানানো গল্প লিখে কাটিয়েছি। অনেক সময় সত্যিকার সামগ্রি দিয়ে। ভাবি – যা হয়েছে তা সত্যি বটে। যা হয়নি, কিন্তু যে কোনও সময়ে হতে পারে – তাই বা মিথ্যে হবে কেন?” তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এ তো আমাদেরও বিশ্বাস, “পৃথিবীর ভালবাসার জায়গাগুলো অর্ধেক মাটি দিয়ে গড়া আর অর্ধেক মনগড়া।” লিখছেন, “মানব জীবনের সব কীর্তিই তৈরি হয় মনের মধ্যে। তারপর তাকে শাবল দিয়ে খুপরি দিয়ে হাতুড়ি–বাটালি-ছেনি দিয়ে, ওলন দিয়ে দোলন দিয়ে, মাপকাঠি দিয়ে, হাত দিয়ে, পা দিয়ে, চোখ-কান দিয়ে, গলা দিয়ে, যেখানে যার স্থান সেখানে নামানো হয়।”
তাই দু’জনের ক্ষেত্রেই ছোটদের তন্ময় জগতের নানা ‘আজগুবি’ সব যেন সত্যি হয়ে ধরা দিচ্ছে। এই আজগুবিই আসলে সৃষ্টির উঠোনটি। আর দু’জনেরই থেকে থেকে একই যাচাই – লেখক হওয়া হচ্ছেই, কারণ ওটাই তো একমাত্র সম্ভব। লীলার জন্ম ১৯০৮, আর মার্কেস ১৯২৭। লীলা মজুমদার আমার দিদিমার বয়সি আর মার্কেজ আমার মায়ের থেকে ঠিক এক বছরের বড়। একেবারে এক প্রজন্মের তফাৎ। সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপট, কিন্তু ওই একটা বাড়ি, ওই একটা বাগান, ওই একটা মানুষ আর সব ছাপিয়ে ওই একটা মন। মনে হয় যেন একই ঘরের দু’পাশের দুই জানলায় পিঠ ঠেকিয়ে দু’জনে বসেছেন নিজেদেরই পুনর্বাসনের এক ‘আজগুবি’ আয়েশে। দু’জনের চোখই যে একই রকম ‘জ্বলজ্বলিং!’
সম্প্রতি, হাজির হয়েছিলাম লীলা মজুমদার স্মারক বক্তৃতা শুনতে। কী মজা লাগছিল, তাঁরই স্মৃতি কথায় এই কয়েক বছর আগেও যারা ‘দিন দুপুরে’, ‘মাকু’, ‘টংলিং’ তারাই বুড়ো বুড়ি হয়ে আমোদ করছে। খুব গর্বও হচ্ছিল এই ভেবে যে, সেই কবেকার ‘সন্দেশ’ থেকে হালের প্রকাশক ‘লালমাটি’ অবধি তিনি বিছিয়ে আছেন আপন মহিমায়। তবে শুধুমাত্র তাঁর রচনার সঙ্কলন করে রচনাবলি প্রকাশই যথেষ্ট নয়, চাই আরও নানা রকম পরিমার্জনাও। কত মানুষ, কত প্রতিষ্ঠান আর কত পত্রিকা এবং প্রকাশক। তবু ভাবায় প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত হয়ে কেন মহাশ্বেতা দেবী বা তাঁর পরের লেখকদের নামে আনাগোনা নেই! সমসাময়িক আশাপূর্ণা আছেন কিন্তু একটু পরের, অমৃতা প্রীতম, প্রতিভা বসু, সুকুমারী ভট্টাচার্য, কল্যাণী দত্ত এবং রাণী চন্দ কেন নেই! তাঁর লেখার সঙ্গে সঙ্গে একটি জীবনী পঞ্জী এবং ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উল্লেখপঞ্জীও খুব জরুরি। এ থেকেই উঠে আসবে এক বহুমাত্রিক সমাজ-মন আর চিন্তাভ্যাসেরও ইতিহাস। এ কাজটুকু করে ফেলতে না পারলে সুতো ছেঁড়া ঘুড়ির মতোই উড়তে উড়তে মিলিয়ে যাবে কালের গর্ভে। প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে তাঁর লেখার প্রসাদগুণ কমবেনা কারণ, পাঠকদের জন্য তো রইলই সেই সোনার ফসল, ঝাঁকে ঝাঁকে ফুটে থাকা তাঁর প্রিয় ‘ভায়োলেট!’
আড্ডা আর একা থাকা,দুটোই খুব ভাল লাগে।
লিখতে লিখতে শেখা আর ভাবতে ভাবতেই খেই হারানো।ভালোবাসি পদ্য গান আর পিছুটান। ও হ্যাঁ আর মনের মতো সাজ,অবশ্যই খোঁপায় একটা সতেজ ফুল।




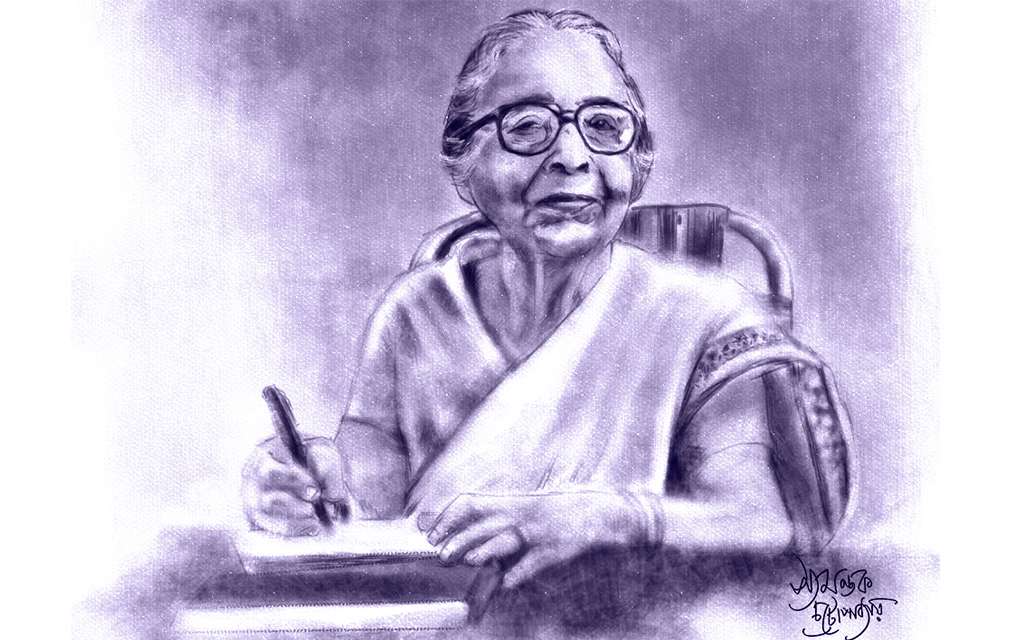



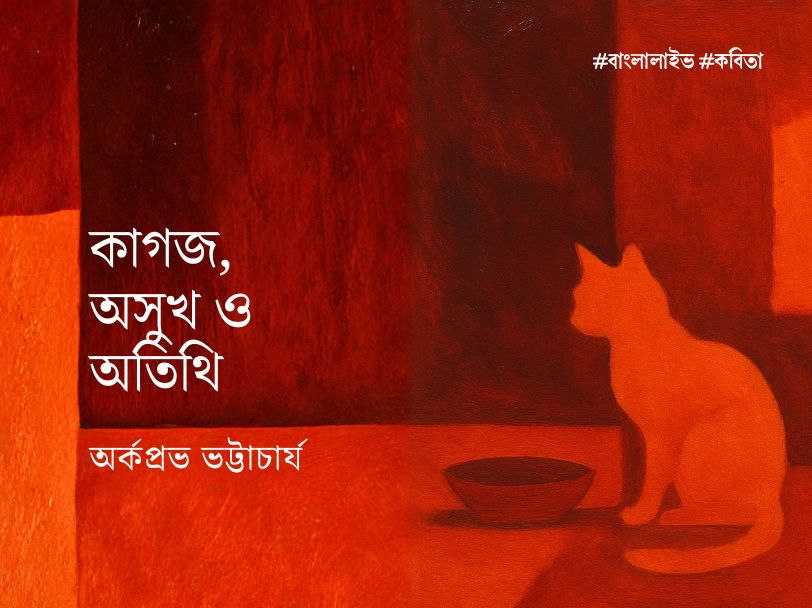


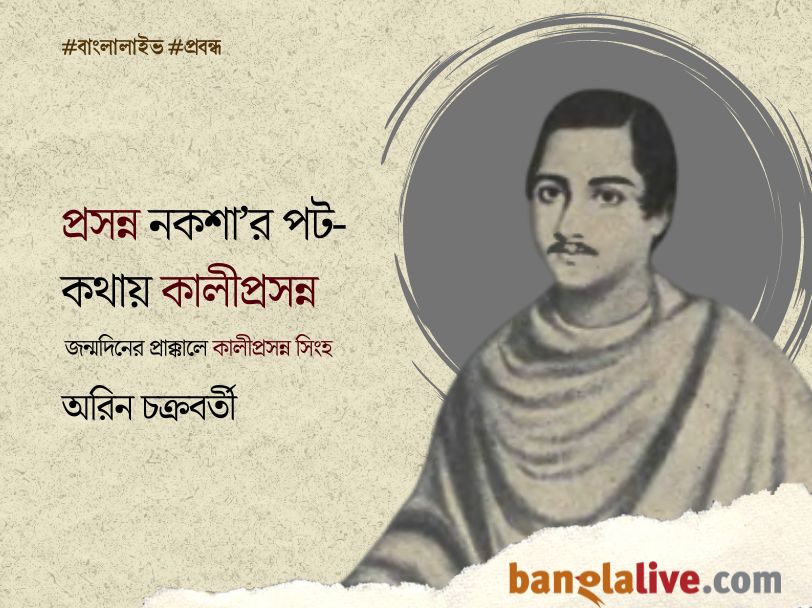




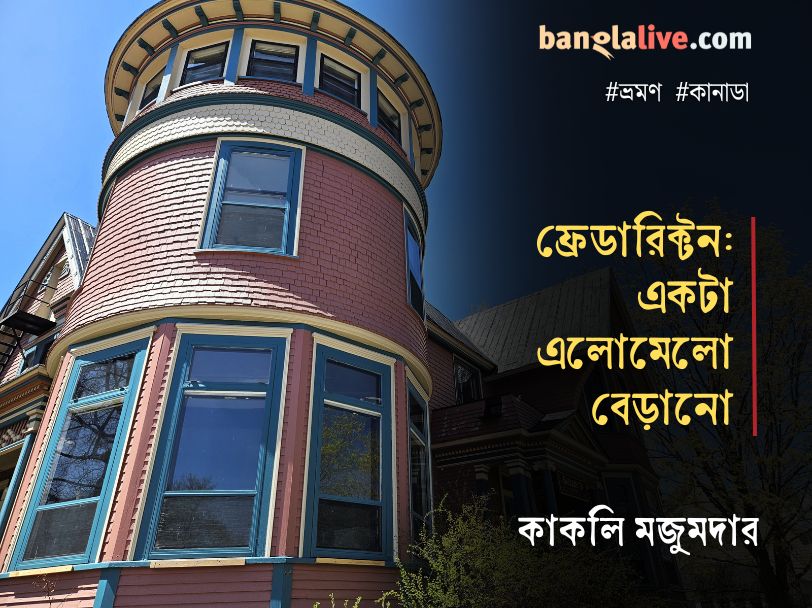
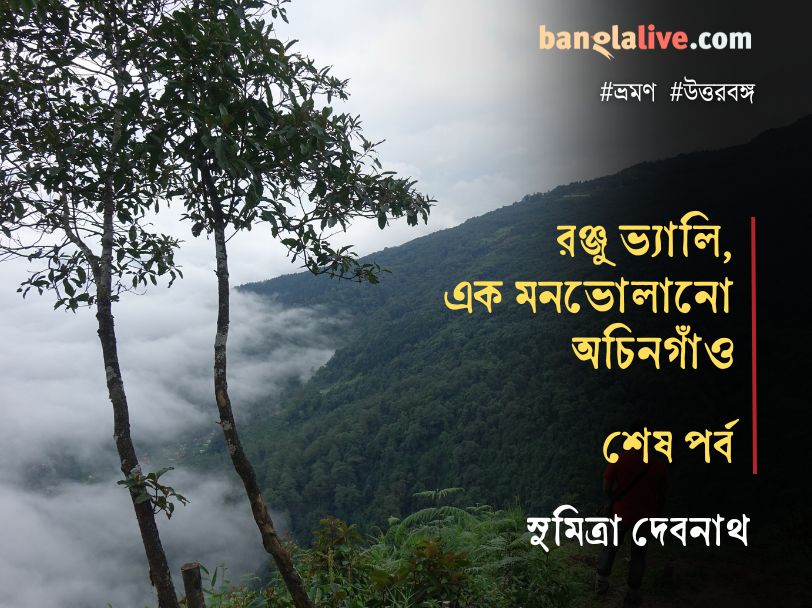








4 Responses
কী সুন্দর লিখেছেন। খুব ভালো লাগলো।
অনেক ধন্যবাদ।
lila majumder ke nie emon lekha kokhono porini. khub sundar.
তাই! আমার কাজই তো চেনা চৌকাঠটা টুক করে পার হয়ে যাওয়া