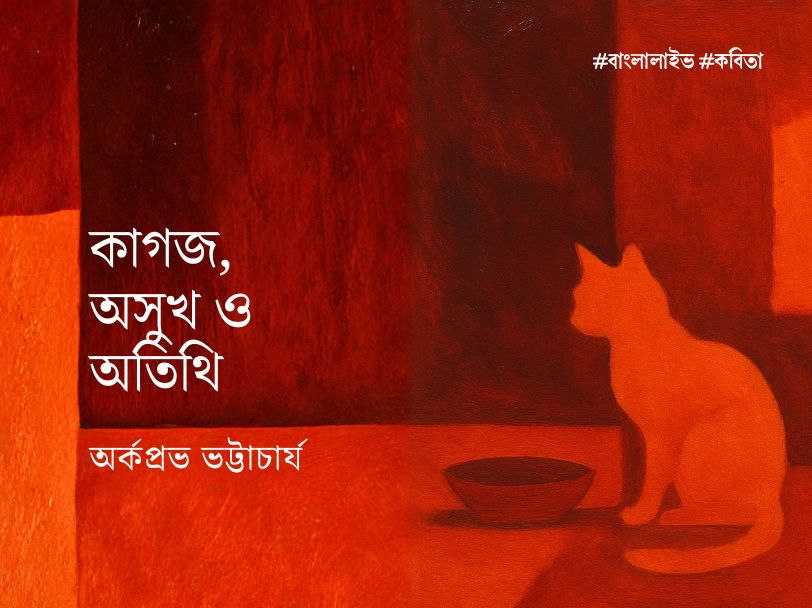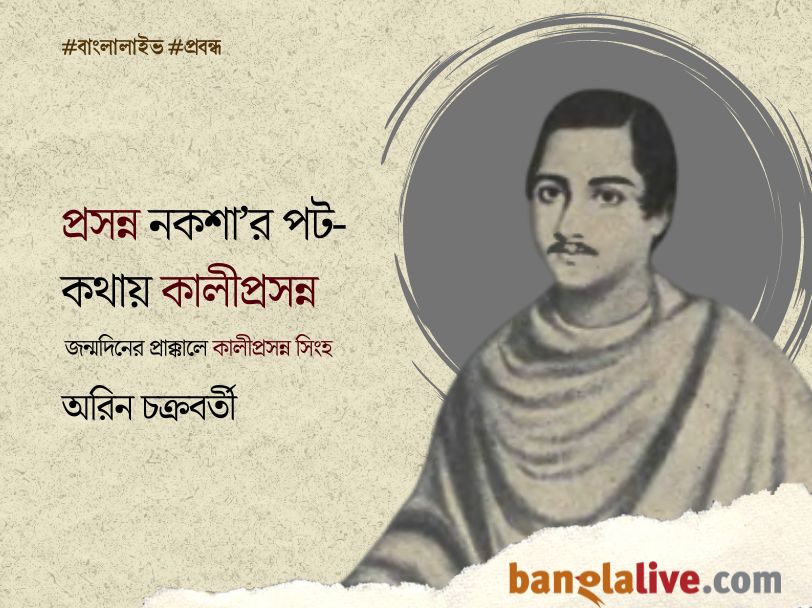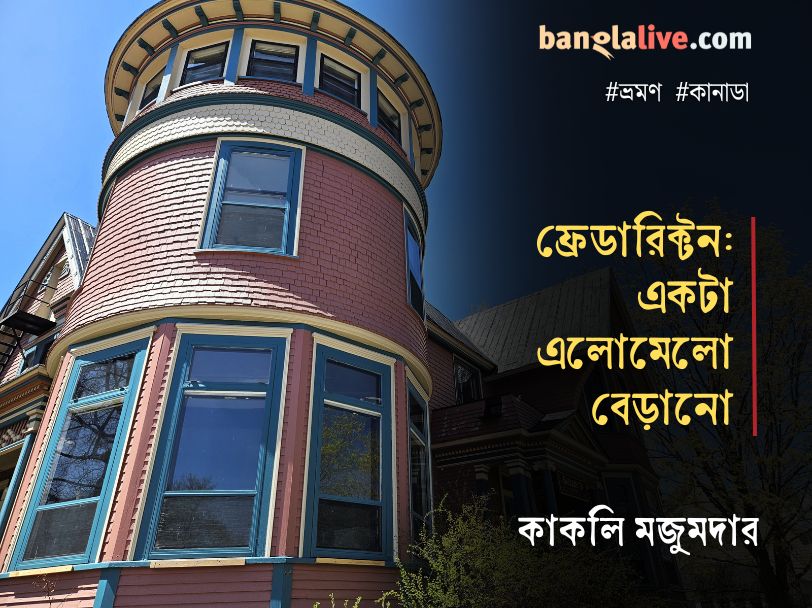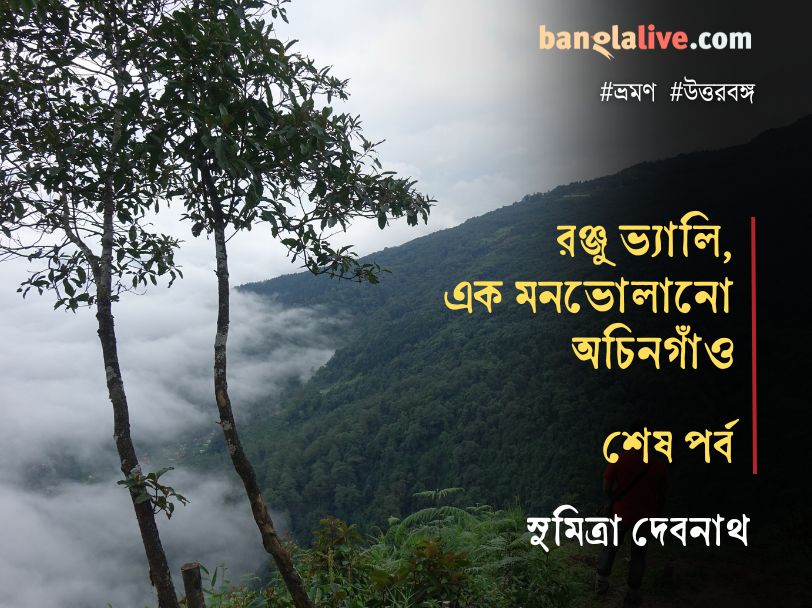দুর্গাপুজোর বোধন থেকে বিসর্জন। সবেতেই ভোজন হল বিশেষ অনুষঙ্গ।
বিসর্জন শব্দের অর্থ হল বিশেষ ভাবে অর্জন, তাই দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জন করে বিজয়ায় মা-কে ত্যাগ নয়, বিশেষরূপে অর্জন। খাওয়াদাওয়াতেও সেই “বিশেষ” রেশটুকুনি ছুঁইয়ে পুজোর স্মৃতিকে জিইয়ে রাখা। শারদীয় উৎসব শেষের মনখারাপের আগেভাগেই সুখাদ্য দিয়ে সব ঢেকে দেওয়া। সবটুকুনিতেই বাঙালির রসনাবিলাস থইথই পসরায় পরিপাটি থাকে যেন। মায়ের আসা আর যাওয়াই সার। তার মধ্যেই সম্বচ্ছরীয় ব্যুটিক রান্নার সম্ভারে হেঁশেলের চাদ্দিকে ভরভরন্ত সুখাদ্যের সম্ভার। ষষ্ঠীর সকালে লুচির খোলায় তার শুরুয়াত আর বিজয়াদশমীর সিদ্ধির শরবতে তার পরিসমাপ্তি।
[the_ad id=”266918″]
একদিকে হেঁশেলের বৈচিত্র্যময়তা অন্যদিকে বারব্রত-স্ত্রী আচার। এই পাঁচটা দিনে যেন সুগৃহিণীদের আঁটুপাটু পরাণ। ষষ্ঠীর ভোর শুরু হয়েছিল ব্রতকথা পড়ার আগে দরজার মাথায় তেল-হলুদ-সিঁদুর দিয়ে বসুধারা এঁকে। পাঁচদিন ধরে কবজি ডুবিয়ে রাঁধাবাড়ার এলাহি আয়োজনের পর দশমীর সিঁদুরখেলায় সামিল হবার আগেও হেঁশেল রাজ্যপাটে সেদিন বিশেষ তোড়জোড় শুরু হয়ে যেত ভোর ভোর। নবমী নিশির ধুনুচিনাচের শেষেই ঘুগনির মটর ভেজানোর কথা মাথায় রাখতে হত।
ঘুগনি? এখনকার একটি বাচ্চা সে বার বিজয়ার ঘুগনি হাতে নিয়েই বলে উঠল, ইয়েলো পিজ় কারি? ইয়েলো পিজ় হয় মা? পিজ় তো গ্রিন। তার মা তাকে বোঝাতে বসলেন তখন। সবুজ মটর পাকলে তা হলুদ মটর হয়। তা দিয়েই এই ঘুগনি বানায়।

বিজয়ার ঘুগনি মানেই হয় পাঁঠার মাংসের কিমা পড়বে তাতে আর নয়তো হবে পিঁয়াজ-রসুন-আদা-টোম্যাটো দিয়ে। তবে দুয়েতেই নারকোল কুচি মাস্ট। তখন সারাবছর ধনেপাতা পাওয়া যেত না। তাই জিরে-লঙ্কা শুকনো খোলায় নেড়ে নিয়ে হামানদিস্তায় গুঁড়ো করে আগেভাগেই শিশিবন্দি হত সেই বিশেষ ঘুগনির জন্য। এক বন্ধুর বাড়িতে বিজয়া করতে গিয়ে কপাল জোরে পেয়েছিলাম ঘুগনির নিচে একটি আগজ্বলন্ত আলুর চপ। অভিনব কায়দা। মানে এখনকার আলুর টিকিয়ার ওপর ঘুগনির পরিবেশনায় যেমন চাটের ছোঁয়া তেমনি আর কি।
বিজয়া দশমীর দিনে পোলাও-পাঁঠার মাংস কিম্বা মাটন বিরিয়ানি হত দুপুরবেলায়। সেই মাংস আনার লাইন দিয়েই গৃহকর্তা কিছুটা মাংসের কিমাও রেডি করে আনতেন বাজারের থলির মধ্যেই। নারকোল কুচি ভেজে নিয়ে, ডুমো ডুমো করে আলু দেওয়া কী অপূর্ব মায়ের হাতের সেই ঘুগনি। আমরা তাকিয়ে থাকতাম, কখন মা বলবে একটু চাখতে? কেউ বিজয়া করতে এলে গরম ঘুগনির ওপরে জিরেভাজার গুঁড়ো ছড়িয়ে, ঝিরিঝিরি করে কাটা পেঁয়াজ, লঙ্কা আর লেবুর রস দিয়ে সেই ঘুগনি পরিবেশন করা হত নিমকি আর নাড়ুর সঙ্গে। স্পেশ্যাল গেস্ট এলে সেই ঘুগনি পরিবেশিত হবে খানকয়েক ফুলকো লুচি সহযোগে।

সোনার মত আখের গুড় জাল দিয়ে কড়াপাকের নাড়ু হত। গুড় জাল দেওয়ার সুঘ্রাণে ম ম করত সারাবাড়ি। তার মধ্যে নারকেল কোরা দিয়ে পাক হত যতক্ষণ পর্যন্ত না কড়ায় লেগে যায় অল্প, রং দেখে চিনতেন মায়েরা। সেই নাড়ুর মধ্যে ছোট এলাচের গুঁড়ো আর এক ফোঁটা কর্পূরের গন্ধ যেন এখনো নাকে লেগে রয়েছে। সামান্য ঘি হাত করে নিয়ে তেলোয় করে গরম অবস্থাতেই সেই নাড়ু পাকানো হবে। সেটাও নাকি একটা শিল্প। মা বলতেন। সবকটি নাড়ু হবে নিটোল গোল, মসৃণ এবং সমান সাইজের। কেউ আবার বানাত নারকোল দিয়ে চিনির পাকে নরম নরম রসকরা। সেও যেন অমৃত।
দুপুর থেকে কাঠের জ্বালে মায়ের ক্ষীর বসানো? তলা লেগে যাওয়া ঘন দুধের মধ্যে নারকোল বেটে পুর হবে চন্দ্রপুলির। ঠাকমার সঙ্গে বসে আমাদের এলোঝেলো, কুচো নিমকি, নারকেল নাড়ু আর চন্দ্রপুলির সহজপাঠ নেওয়ার শুরু। প্রথম খোলার নাড়ু, চন্দ্রপুলি বানিয়েই আগেভাগে তুলে রাখা হত কোজাগরী লক্ষীপুজোর জন্য একটা মাটির হাঁড়িতে।
[the_ad id=”266919″]
তাল তাল ময়দা মাখা হত কষে ময়ান দিয়ে। কুচো নিমকির জন্য। ধবধবে সাদা ময়দার তালে ফুটে উঠত কালোজিরের রহস্য। এক টুসকি খাওয়ার সোডার সঙ্গে দু’ এক ফোঁটা পাতি লেবুর রস দিতেন মা। মুচমুচে আর খাস্তা হবে বলে। কাঠের বারকোশের ওপর পাতলা করে নিমকি বেলে ছুরি দিয়ে কেটে জড়ো করা হত। চাকির ওপর তেরছা করে নিমকি কাটাও একটা আর্ট। মায়ের পছন্দ না হলে রেগে যেতেন। আমরা ডালডায় ভাজা নিমকি দেখিনি। লক্ষ্মী ঘি কিম্বা ভাদয়া। তারপরেই পোস্টম্যানের যুগ এসে গেছিল হুড়মুড়িয়ে।

ছোটোপিসি শিখিয়েছিলেন তিনকোণা নিমকি বানাতে। প্রতিটি নিমকি লুচির মত গোল এবং ফিনফিনে পাতলা বেলে নিয়ে ফুটন্ত তেল বা ঘিয়ের মধ্যে ছাড়ার সেই কৌশল রপ্ত করেছিলাম সেবার। দু’হাত লাগাতে হবে। একহাতে খুন্তি আর অন্যহাতে সাঞ্চা দিয়ে গরম তেলে ছেড়েই চার ভাঁজ করে তিনকোণা নিমকিকে চেপে ধরে রাখতে হবে, সে যাতে না ফোলে। তারপরেই দুপিঠ আঁচ কমিয়ে মুচমুচে করে ভেজে নিয়ে তেল ঝরিয়ে তুলে রাখার পালা।
সেদিন সিঁদুর খেলতে যাওয়ার আগেভাগেই মায়ের রান্নাঘরের রাজ্যপাট থৈ থৈ হত সব মুখরোচকে। রান্নাঘরের লোহার শেকল সন্তর্পণে তুলে দিয়েই মা তখন লাল পাড় গরদের শাড়ি, গলায় পাটিহার আর কানপাশা, হাতে রূপোর রেকাবে পানের খিলি, বরণের জন্য পানপাতা, ধানদুব্বো, সিঁদুর কৌটো আর সন্দেশ নিয়ে তৈরি। মায়ের সিঁদুর খেলার প্রস্তুতি তখন তুঙ্গে। আমরা থাকতুম সেই মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষায়। চুপিচুপি, টিপটিপ পায়ে শেকল খুলে বয়ামে রাখা একমুঠো নিমকি আর চাড্ডি নারকেল নাড়ু কোঁচড়ে নিয়ে চিলেকোঠায় একছুট।
[the_ad id=”270084″]
মামারবাড়িতে দিদিমার সে এক যজ্ঞি বিজয়ার দিনে। সে এক হৈ হৈ কান্ড বাড়িতে! বিশাল রান্নাঘরের মধ্যে কয়লার উনুন জ্বলছে গাঁকগাঁক করে। ষণ্ডামার্কা লোকজন বড়বড় কাঠের বারকোশে কলাপাতা বিছিয়ে নারকেল কুরছে। উনুনে কালো লোহার কড়াইতে দুধ ঘন হচ্ছে। নারকেল কোরা নিয়ে শিলে বাটতে বসেছে একজন। দুধ আধা ঘন হয়ে এলে নারকেল বাটা দিয়ে যাচ্ছে আর একজন। আর দিদা বসে কাঠের খুন্তি দিয়ে দুধ আর নারকেল পাক দিচ্ছে। দুধের ক্ষীর আর নারকেল বাটার মিশ্রণটি মসৃণ করে এবং সমানভাবে মিশিয়ে দিয়েই চলেছে দিদা। কি অসম্ভব মনের জোর সেই বয়সে!

কী সুন্দর হেঁশেল পারিপাট্য!
এবার কাজের মেয়ে এসে ছোটএলাচের গুঁড়ো, চিনি, বড়এলাচের দানা আর কিশমিশ রেখে গেল। দিদার তখনও কাঠের খুন্তি-লোহার কড়াইতে যুদ্ধ চলছে তো চলছেই। সারাবাড়ি ম ম করছে চন্দ্রপুলির আগাম আগমনী বার্তায় আর মা দুর্গার বিজয়ায়। এবার চিনি পড়ল কড়াইতে। আরও জল বেরুল বুঝি। মনযোগ আর অধ্যাবসায় একাত্ম হয়ে ঘনীভূত হল চিনি-নারকেল-ক্ষীরের সমুদ্রে। এবার কড়াইয়ের গায়ে লাগা লাগা গন্ধ। একটু বুঝি তলা ধরল। দিদা বলে উঠলেন “তোরা কি পোড়া পোড়া গন্ধ পাচ্ছিস?” তার মানে পাক ঘন হয়ে এল। এবার ছোট এলাচের গন্ধবাতাস রান্নাঘর জুড়ে। দু’জন ষণ্ডামার্কা লোক এসে পেল্লায় লোহার কড়াইটাকে নামিয়ে দিল মাটিতে। তারপর সোনার মত চকচকে করে মাজা পেতলের পরাতে ঘি মাখিয়ে ঢেলে দিল চন্দ্রপুলির পুর।
[the_ad id=”270085″]
এবার গড়ার পালা।
হাতের তেলোয় একফোঁটা ঘি মাখিয়ে তেলতেলে করে নেওয়া আর ছাঁচে ফেলে একে একে সুদৃশ্য চন্দ্রপুলি গড়ে ফেলা। মাথায় একটা করে বড় এলাচের দানা আর একটা করে কিশমিশ গুঁজে দেওয়া।
ব্যাস্! এই চন্দ্রপুলি যেন একটি সম্পূর্ণ শিল্পকলা। কোনওটা অর্ধচন্দ্রের মতো, কোনওটা কলকা, কোনওটা আবার চৌকো।
কাঠের ছাঁচ, কালো পাথরের ছাঁচ কত কী ছিল দিদার কাছে!
মামাবাড়িতে দ্বারিক ঘোষের ঘিয়ে ভাজা ক্ষীরের চপ আর সেন মশাইয়ের মিহিদানার সঙ্গে বাড়ির বানানো এই অভিনব চন্দ্রপুলি বিজয়ার মিষ্টি হিসেবে দেওয়ার রেওয়াজ দেখেছি।
দশমীর বিকেলে পাড়ার ঠাকুর গঙ্গায় বিসর্জন হয়ে গেলেই বাবা আমাদের কলাপাতার পেছনে লালকালি দিয়ে “শ্রী শ্রী দুর্গা সহায়” লেখাতেন। দশমীর কোলাকুলি, প্রণাম পর্ব সমাধা হলেই দেউড়িতে বাবাদের বিজয়ার মজলিশ বসত। আমাদের আড়িয়াদহের বাড়িতে বিশাল হাঁড়িতে সিদ্ধির শরবত তৈরি হত। এখন লোকে বলে ঠান্ডাই। আমরা সত্তরের দশক থেকেই এর স্বাদ পেয়েছি। আমাদের ভাগেও মিলত একটু করে, গোলাপফুলের সুগন্ধী পাপড়ি দিয়ে গারনিশ করা আর আমাদের জন্য সেই রেশন করা শরবত। ঠাকুরদার সাদা পাথরের গেলাসে, বড়দের বড় মাপের গেলাসে। ছোটদের জন্যে ছোট্ট কাপে। মন ভরত না আমাদের। মনে হত আরও একটু পেলে কী ভালোই না হত! কিন্তু আমরা ছিলেম নির্বিবাদী।

বিজয়া মানেই এই বিশেষ শরবত। আগের দিন রাতে ভিজিয়ে রাখা শুকনো সবজেটে সিদ্ধিপাতা ভিজিয়ে রাখা হত। সিদ্ধিপাতা নাকি খোলা বাজারে আইনত বিক্রি হয় না। আবগারি দফতরে কে একজন চাকরি করতেন। তিনি এনে দিতেন। দুধে ভেজানো কাঁচা চিনেবাদাম, পেস্তা, গোলমরিচ আর মৌরি একসঙ্গে শিলনোড়ায় বাটা হত। ভেজানো সিদ্ধিও শিলে পিষে নিয়ে বিশাল হাঁড়ির মধ্যে একসঙ্গে তরিজুত করে মেশানো হত ঠান্ডা দুধের সঙ্গে। তারপর তার মধ্যে পড়ত চিনি। বাজার চলতি ক্ষীরের পেঁড়া গুলে দেওয়া হত সেই মিশ্রণে। যত মিষ্টি ঢালবে ততই চড়বে নেশার পারদ।
বরফ আনা হত বাজার থেকে। ফ্রিজ তো ছিল না বাড়িতে। আমাদের কাছে বরফ ছিল অত্যাশ্চর্য এক দুষ্প্রাপ্য জিনিস। এবার বরফকুচি দিয়ে সেই হাঁড়ির মধ্যে ফেলা হত আগেকার একটি তামার পয়সা। তামার সঙ্গে পুরো সিদ্ধির শরবতের নাকি অসাধারণ এক রসায়ন আছে। তামার গুণে সিদ্ধিতে নাকি দারুণ নেশা হয়। এসব রহস্য পরে জেনেছি।
[the_ad id=”270086″]
সন্ধ্যে হলেই বাড়ি পরিক্রমায় বেরোতাম আমরা। বিজয়ার পেন্নাম তো ছুতো। কার ভাগ্যে কী জোটে সেই আশায়!
ও পাড়ার দুর্গাদিদা, সে পাড়ার শঙ্করীদাদুদের বাড়িতে আমাদের হাত দিয়ে মিষ্টি পাঠাত মা। কেউ একমুঠো কুচো গজা, কেউ একটা পেরাকি, কেউ আবার দু’চামচ মিহিদানা… আবার কেউ খাওয়াত এলোঝেলো। সেই খেয়েই বিজয়ার রাতে আমাদের উদরপূর্তি হত। পরদিন মায়ের হাতের বাসি ঘুগনি আরও জমে যেত সেই ফাঁকে।
রসায়নের ছাত্রী ইন্দিরা আদ্যোপান্ত হোমমেকার। তবে গত এক দশকেরও বেশি সময় যাবৎ সাহিত্যচর্চা করছেন নিয়মিত। প্রথম গল্প দেশ পত্রিকায় এবং প্রথম উপন্যাস সানন্দায় প্রকাশিত হয়। বেশ কিছু বইও প্রকাশিত হয়েছে ইতিমধ্যেই। সব নামীদামি পত্রিকা এবং ই-ম্যাগাজিনে নিয়মিত লেখেন ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনি, রম্যরচনা ও প্রবন্ধ।