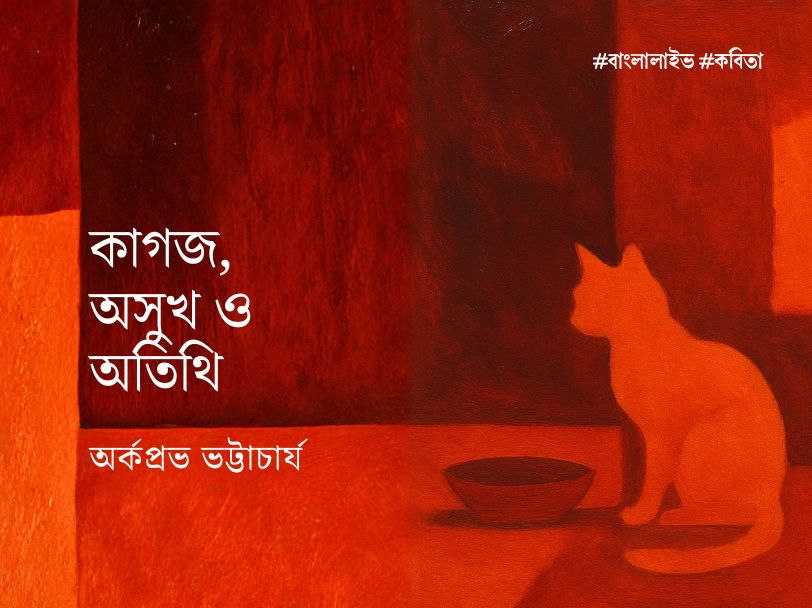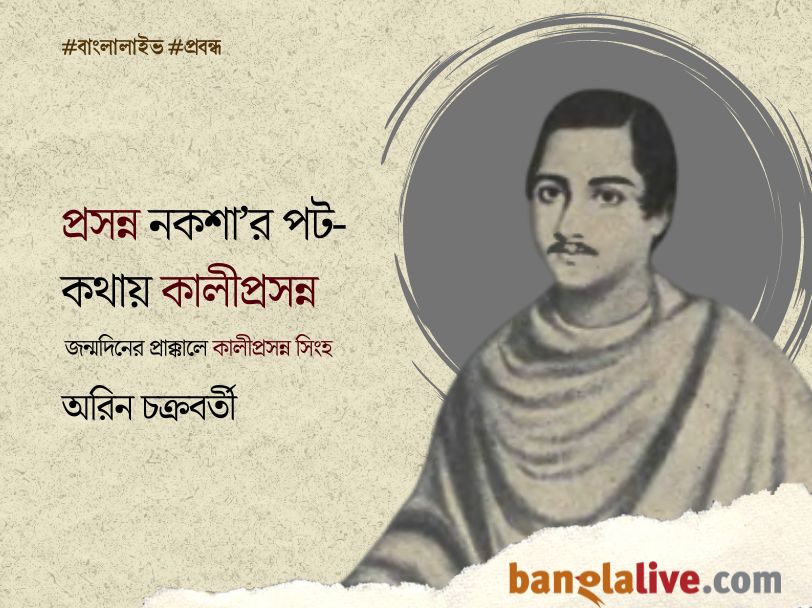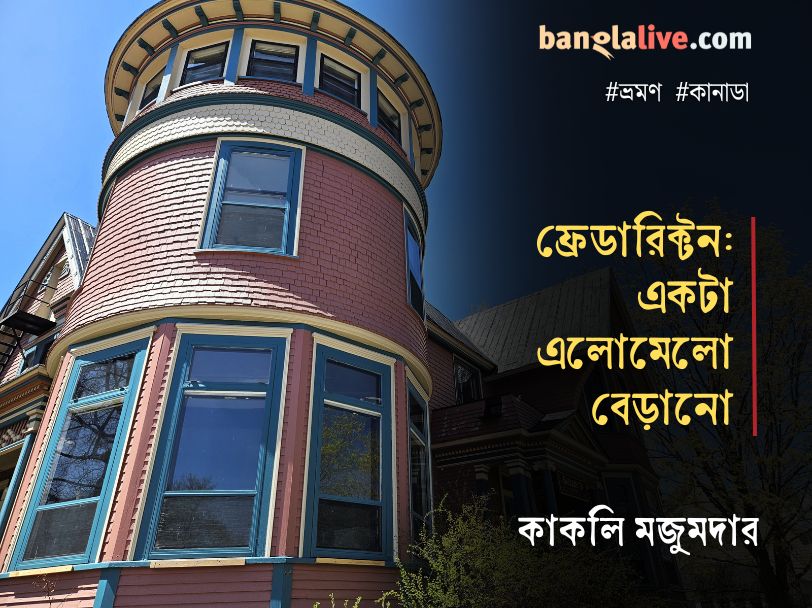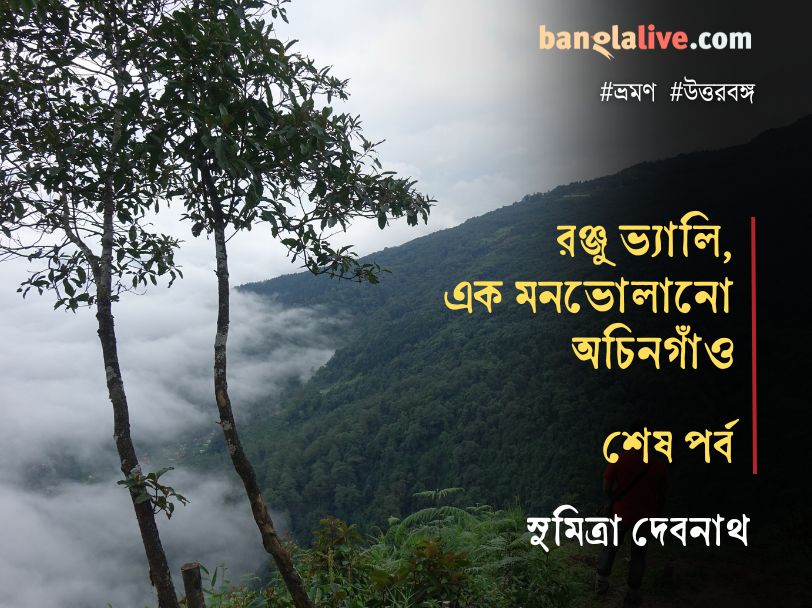আগের পর্বের লিংক: [১] [২] [৩] [৪] [৫] [৬] [৭] [৮] [৯] [১০] [১১] [১২] [১৩] [১৪] [১৫] [১৬] [১৭] [১৮]
জমিদারের কথা খানিক আরও না বললেই নয়… মন্দিরতলা বা মন্দিরের মাঠ তাঁর জমিদারি ছিল, এমনটা অনেকেই ঠাট্টাবিদ্রুপে বলেছে— “কইতাননি লিজে নিছেন না বাপ-ঠাকুর্দার লগত পাইছেন? আপেনেরেই জমিদার মানায়, যেমন উঁচা শরীল, তেমন উঁচা গলা৷ পাকিস্তান থেইক্যা খেদা খাইয়া সবাই যখন ভাগে, আপনে যে কী কইরা আস্তা জমিখান লগে লইয়া আইলেন ভাইবা পাই না৷” বাঁদর বা ভালুকের খেলা দেখাতে যারা আসত, অনুমতি নিতে হত তাদেরও৷ আধঘণ্টা কি একঘণ্টা খেলা দেখিয়ে চলে যাবে, তা হোক, অনুমতি ছাড়া মাঠে ঢোকা যাবে না৷ —”কে না কে কইত্থেইকা না কইত্থেইেকা আইল আর মাঠে ঢুইকা পড়ল, এইটা হইতে দিমু না৷ একটা দুষ্টলোক একশোটা লোককে নষ্ট করতে পারে৷ বাইরঅ৷ পালা৷” সাড়ে ছ-ফুট উঁচু হাড্ডিসার কাঠামো লাঠি নিয়ে তেড়ে আসত৷ তখন জমিদার ভোরের সবজি বিক্রেতা, দুপুরে কুল বা তালশাঁস বেচেন, বেশিরভাগ সময়টা মন্দিরতলায় থাকেন৷
আরও একটা ব্যাপার হয়তো ছিল৷ দেশ গেছে, ঘরবাড়ি গেছে, ফরিদপুরের চৌকিদারিটা কিন্তু যায়নি৷ অপরাধী খুঁজে-ফেরা, এ পাড়ায় ও পাড়ায় শান্তির দায়িত্ব নিয়ে হেঁটে-চলা সেই মানুষটিকে তিনি নিজের ভেতরে যত্নে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন৷ গৌরাঙ্গ রায় তাঁকে ইট-বালির গোলা পাহারা দেবার জন্য আনেন বলে জানা যায়৷ গৌরাঙ্গ রায় মারা গেলে এবং সেই ব্যবসা উঠে গেলে পাহারা ফুরিয়ে যাবারই কথা৷ তেমনটা হয়নি৷ পাঁচিলহীন খোলা জমির পবিত্রতা রক্ষার দায় স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন ভবা চৌকিদার৷
বাঁদিকে দু-মিনিটের দূরত্বে গির্জা৷ বিশ্বাসীরা আসে নিয়মিত৷ সেটা পাঁচিল ঘেরা৷ ডানদিকে তিন মিনিট দূরে মসজিদ, সেটাও সুরক্ষিত৷ বিশ্বাসী মানুষজনের আসাযাওয়া প্রত্যহ৷ শিবমন্দির ও তার লাগোয়া জমির পাঁচিল নেই। দেখভাল করার কেউ নেই। মন্দিরে পুজো হয় বছরে একবার৷ এখানে যা-খুশি হতে পারে, যখন তখন৷ বিশেষ করে, পাড়াটা ভালো নয়, সময়টাও ভালো নয়৷ বস্তিঘরের কাঁথাকানি চটচাটাই বালিশ-তোষক অমূল্য সম্পদ৷ এসবের সুরক্ষা ও পবিত্রতা রক্ষা জরুরি৷ অনাচার হতে দেওয়া যায় না৷ ময়লা জমতে দেওয়া যায় না৷ জমিদখলের ফন্দিফিকিরবাজ মানুষ ছিলেন না ভবা চৌকিদার৷

এখানে বলে রাখা মনে হয় দরকার, এককালে ডিহি শ্রীরামপুর অঞ্চলের একশো শতাংশ বাসিন্দাই ছিল মুসলিম ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের৷ হরেন মুখার্জির পিতৃদেব যখন জমি কিনে বাড়ি করেন, পূর্ব কলকাতার এই এলাকাটি ছিল অনুন্নত ও দীনদরিদ্র মানুষের বসতি৷ হিন্দুরা এখানে বসবাস শুরু করে সম্ভবত দেশভাগের কিছু আগে৷ মুসলমানদের বাড়িগুলো সম্পত্তি বিনিময়ের মাধ্যমে হিন্দু-বাড়ি হতে থাকে৷ এই কারণে এখানে গির্জা ছিল, মসজিদ ছিল, কিন্তু মন্দির ছিল না৷ টিনের ঘরের মন্দির কে কবে বানিয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না৷ মন্দির বানানোর পেছনে জমিদখলের বুদ্ধি থাকতে পারে৷ হতেই পারে সেই বুদ্ধিধর মানুষটি ইট-বালির কারবারি গৌরাঙ্গ রায়ের আগেকার লোক।
মন্দিরতলা বা মন্দিরের মাঠ আমার মনে অম্লান রুপোলি পরদার ছবি হয়ে জেগে আছে, যেখানে পুজোর পর একমাস রামায়ণ পালা হয়েছিল, যা আমার জীবনের প্রথম রামায়ণ-পাঠ, বইয়ে-পড়া রামায়ণের চেয়ে ঢের জীবিত। সেখানে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ তো আছেই, তাঁদের পাশাপাশি কৈকেয়ী-মন্থরা বালি-সুগ্রীব-জটায়ু মন্দোদরী-সরমা এমনকি রাবণও অনেক বেশি চেনা, প্রাণময়। ম্যারাপের নীচে অযোধ্যা বা লঙ্কার রাজদরবার, পঞ্চবটীবন, অশোককানন— অনেক বেশি সত্য। আর সেই সত্যের পাশে আজও দাঁড়িয়ে থাকেন জমিদার, ঝাড়ু হাতে— নোংরা জমতে দেওয়া যাবে না, সমাজ ময়লা হতে দেওয়া যাবে না৷ —”কাঁথাবালিশ বিছানাপাতি মাঠের ওইধারে দিবেন৷ আমি কইয়া রাখলাম৷ রামায়ণ যতদিন চলব ততদিন আপনেগো ঘরের জিনিস এইধারে রাখবেন না৷ কইয়া দিলাম৷” হারমোনিয়ম-সানাই-বাঁশি-তবলা-ঢোল-ঝাঁঝ ইত্যাদি বেজে ওঠবার আগে ছিদামবাবুর গমভাঙানোর দোকান থেকে চেয়ার অর্থাৎ সিংহাসন নিয়ে আসছেন জমিদার, পরিষ্কার গামছা দিয়ে ঝেড়ে দিচ্ছেন সাদা গুঁড়ো— ছেলেবেলার ঘোরলাগা চোখ দেখতে পায় আজও৷

শান্তাদিরা যখন রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী করেন, সম্ভবত জন্মশতবার্ষিকী, তখন জমিদার অন্য কোথাও কোনও কাজে লেগেছেন৷ মন্দিরের মাঠে তাঁকে দেখা যায় কম৷ তাঁর অনুপস্থিতির ছাপ পড়েছে মাঠে৷ রেশনের দোকানের লাইনে দাঁড়ানো লোকজন খাবার খেয়ে ঠোঙা ফেলে মাঠে, কলার খোসা পেয়ারার ছিবড়ে ইত্যাদি বাতিল জিনিস ছুড়ে দেয়, টিনের ঘরের আড়ালে টয়লেট করে৷ টের পান তিনি৷ চেঁচামেচি করেন৷ অনির্দিষ্ট অতিসাইরা, খাচ্চর, ভাদাইম্মাদের গাল পাড়েন৷ তবে দাপট একটু মিয়োনো৷
শান্তাদিদের অনুষ্ঠানের দিন সারাক্ষণ মন্দিরের মাঠে ছিলেন জমিদার৷ পাড়ার দাদারা দাবড়ে দিয়েছেন৷ এটা কারণ হতে পারে৷ গাঁজা খেতে এখানে বাইরের লোক আসে এ খবর জানাজানি হয়ে গেছে৷ এটাও কারণ হতে পারে৷ কারণ যাই হোক, জমিদারকে সাধারণত যে পোশাকে দেখা যায় না, সেই ধুতি-জামা পরে সেদিন প্রায় সারাটা সময় তিনি দাঁড়িয়েছিলেন মঞ্চের পাশে৷ ছোটদের আবৃত্তির পর, গানের পর সবাই হাততালি দিলে তিনিও হাততালি দিয়েছেন৷ এই জমিদারকে আমরা চিনি না৷ তাঁকে কখনও হাসতে দেখিনি আগে৷ রত্না সরকারের ছোট ভাই, আমরা ডাকতাম ‘বাবুমামা’ (ভালো নাম শেখর, পদবি মনে নেই) এতক্ষণ তিনি তবলা বাজিয়েছেন ছোটদের সঙ্গে, এরপর গাইলেন রবীন্দ্রনাথের গান৷ আমাদের ছোট মাঠ আর ছোট থাকল না৷ বড় একটা কিছুর সঙ্গে জুড়ে অনেক বড় হয়ে গেল৷ এরপর নাটক ‘রবীন্দ্রনাথ’৷ যতদূর মনে করতে পারি, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা৷ অভিনয় করেছিল বেনিয়াপুকুর স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা৷ সেখানে এরকম সংলাপ ছিল: রবিন্দরনাথ বড়া বেওসায়ি থে৷ পুঁজি কম, নাফা বেশি৷ কবিতা লিখতে, গানা লিখতে খরচা কী আছে? খরচা নাই৷ লিখো আর কিতাব ছাপাও৷ বাজারমেঁ কিতাব বেচো৷ পুরা হি পুরা মুনাফা৷ রবিন্দরনাথের গান যে বাজাবে, তাকে পয়সা দিতে হবে৷ গান যত বাজবে তত পয়সা৷ গান যারা গায়, তারাও পয়সা পায়৷ গান যারা শিখায়, তারাও পয়সা পায়৷ সব দিকেই বিজনেস৷ [ষাট বছর আগে বালকবয়সে দেখা নাটকের সংলাপ মনে রাখা বস্তুত অসম্ভব৷ নাটকটির মুদ্রিতরূপ খোঁজ করেছি৷ এখনও পাইনি৷] মনে আছে, তাকিয়ায় হেলান দিয়ে, কানে ফোন নিয়ে ব্যবসায়ী বলেবে, দশ মওন [‘দো মওন’ হতেও পারে] রবিন্দররচনাওলি ভেজ দো৷ বাদমেঁ আউর ভি লাগবে৷ গোটা মাঠ হো হো করে হেসে উঠেছিল৷ মঞ্চের সামনে চটে বসা আমিও হেসেছিলাম৷ অন্যদের দেখে৷ মঞ্চের পাশে দাঁড়ানো জমিদারও হেসেছিলেন৷ হয়তো অন্যদের দেখেই৷ ফোকলা দাঁতের চুপসে যাওয়া গালের হাসি দেখেছিলাম৷ যাঁকে ভয় পাই তিনি হাসলে কত আলো ফুটে ওঠে৷

বালকবেলায় আর-একটা নাটক দেখার আবছা স্মৃতি আছে৷ ক্রিস্টোফার রোডটা রেলপুলে উঠে যাবার আগে ডানদিকে একটা পথ আবাসনে ঢুকে যায়৷ সেসময় নাম ছিল সিআইটি কোয়ার্টারস৷ এখন নাম পালটেছে কিনা জানা নেই৷ এই আবাসন তৈরি হয়েছে আমাদের ছেলেবেলায়৷ শিয়ালদা স্টেশন থেকে বালিগঞ্জ স্টেশনে [পার্ক সার্কাস স্টেশন হয়েছে অনেক পরে] যাওয়ার পথে ডানদিকে৷ তিন নম্বর গোবরা গোরস্থানের লাগোয়া৷ আবাসনে ঢোকবার মুখে ডানহাতে সরকারি দফতর ছিল একটা৷ উদবাস্তুদের ত্রাণ দেওয়া হত৷ অকল্যান্ড অফিস থেকে বিদেশি দুধ আসত৷ চকচকে প্যাকেটে হালকা হলদে রঙের গুঁড়ো দুধ, এখান থেকে বিলি করা হত৷ রাস্তার ওপর তিন-চার ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে আমরা বিনে পয়সার দুধ, রিলিফের দুধ নিতাম৷ দিদিমার সঙ্গে লাইনে দাঁড়াতাম৷ মাথা-পিছু এক প্যাকেট৷ আমরা যেখানে দাঁড়াতাম, তার কয়েক হাত দূরে কাজী নজরুল ইসলামের ফ্ল্যাট৷ তিনি তখন খুবই অসুস্থ৷ সারাদিন খাটে বসে থাকেন৷ কাউকে চিনতে পারেন না৷ সেই ফ্ল্যাটেই থাকেন কাজী সব্যসাচী৷ সে-প্রসঙ্গ পরে বলা যাবে৷
দুধ পেয়েছি কয়েকবার৷ ভারী প্যাকেট, হাত থেকে পড়ে গেছে, ফাটেনি৷ মজবুত৷ সেই দুধ খাওয়া হয়নি কখনও৷ মুদির দোকানে বিক্রি করে দেওয়া হত৷ তীব্র অনটনের সংসারে সামান্য চাল বা ডালের সংস্থান৷ দিদিমা, কিরণবালা বসু, মুক্তাগাছার মেয়ে, কখনও কি ভেবেছিলেন কলকাতার রাস্তায় রোদে পুড়ে নাতির হাত ধরে তাঁকে রিলিফের দুধের লাইনে দাঁড়াতে হবে? এবং খাওয়ার দুধ গোপনে বেচার অন্যায় করতে হবে? দেশভাগ আমাদের সব দিয়েছে৷
তো সেই সিআইটি কোয়ার্টারে নাটক হল৷ ‘রক্তকরবী’৷ মান্টিমাসি নন্দিনী হয়েছিলেন৷ মান্টিমাসি মানে রত্না সরকারের ছোট বোন৷ তাঁর স্বামী মাখনবাবু (পদবি মনে নেই) হেটলি গ্রেশামের শ্রমিক৷ কালিমাখা খাকি হাফপ্যান্ট হাফশার্ট পরে কারখানা থেকে হেঁটে কোয়ার্টারের ফ্ল্যাটে ফিরতেন৷ (এই কোয়ার্টার্সেই থাকতেন গোপাল হালদার৷ কোন প্রক্রিয়ায় এখানে ফ্ল্যাট বরাদ্দ হয়েছিল জানা নেই৷ শ্রমজীবী আর বুদ্ধিজীবী পাশাপাশি৷) বাবুমামা, মানে মান্টিমাসির ছোট ভাই, হয়েছিলেন বিশু পাগল৷ অভিনয় কাকে বলে জানি না৷ মনে আছে, মান্টিমাসি ডাকছেন— ‘বিশুপাগল, পাগলভাই’৷ বাবুমামা গান গাইতে গাইতে মঞ্চে ঢুকছেন৷ ভাই-বোনে কথা হচ্ছে৷ বাবুমামা আবার গান গেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন৷ ‘রক্তকরবী’র কথা বুঝতে পারার বয়সের ধারেকাছে তখন নেই আমি৷ অবাক হয়ে শুধু দেখেছি বাবুমামা মঞ্চে দাঁড়িয়ে একের পর এক গান গাইছেন৷ গান গাওয়া ও গান শোনার একটা ট্রাডিশন ছিল আমাদের বস্তিতে৷ সেখানে বাবুমামাকে দেখেছি তবলা বাজাতে৷ এখানে তিনি গানের মানুষ৷ কথায় কথায় গান৷ গানের মতো কথা৷ মান্টিমাসিকে কখনও গান গাইতে দেখিনি৷ নন্দিনী হয়ে তিনিও গাইলেন৷ মান্টিমাসির চলায় নাচের ছন্দ আগে দেখিনি৷ শান্ত মিষ্টি মান্টিমাসি রাজার মুখে মুখে তর্ক করছেন দেখে অবাক হয়েছি৷ কোয়ার্টার্সের মাঝখানে কাঁকরবিছানো ফাঁকা জায়গায় মঞ্চ বেঁধে ‘রক্তকরবী’ হয় সেবার৷ মঞ্চ বলতে একটা জানালার ছবি মনে পড়ে৷ তার ওপারে রাজা থাকে৷ আজ সেই নাটক নিয়ে কথা বলতে গেলে পড়া-ও-দেখা এবং নিজের মতো করে বোঝা ‘রক্তকরবী’র ছাপ লেগে যাবে৷ ব্যাপারটা সৎ থাকবে না৷ মনে আছে, নাটক শেষ হচ্ছে গান দিয়ে৷ মঞ্চের নীচে বাঁদিকে চেয়ার বসা শান্তাদির ছাত্রছাত্রীরা গাইছে ‘পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে আয়…’৷ মঞ্চের ওপর দর্শকদের মুখোমুখি হয়ে গাইছেন মান্টিমাসি, বাবুমামা ও অন্যরা৷
মঞ্চের সামনে মাটিতে পাতা শতরঞ্চিতে বসে আমি দেখছি৷
ছবি সৌজন্য: লেখক
*পরবর্তী পর্ব প্রকাশিত হবে ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
মধুময়ের জন্ম ১৯৫২ সালে পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহে, কিশোরগঞ্জে। লেখাপড়া কলকাতায়। শৈশব-যৌবন কেটেছে স্টেশনে, ক্যাম্পে, বস্তিতে। গল্প লিখে লেখালেখি শুরু। পরে উপন্যাস। বই আখ্যান পঞ্চাশ, আলিঙ্গন দাও রানি, রূপকাঠের নৌকা। অনুসন্ধানমূলক কাজে আগ্রহী। পঞ্চাশের মন্বন্তর, দাঙ্গা-দেশভাগ, নকশালবাড়ি আন্দোলন নিয়ে কাজ করেছেন। কেয়া চক্রবর্তী, গণেশ পাইন তাঁর প্রিয় সম্পাদনা। প্রতিমা বড়ুয়াকে নিয়ে গ্রন্থের কাজ করছেন চার বছর। মূলত পাঠক ও শ্রোতা।