সারাদিনের কাজের পর তেতেপুড়ে বাড়ি ফিরলে মায়ের কাছ থেকে যে অবধারিত ও অমোঘ প্রশ্নটি শোনা যায়, সেটা বাঙালিমাত্রেই জানেন। ‘কি রে, ভাত খাবি তো?’ ভরদুপুরে কাজে ডুবে রয়েছেন, নাওয়াখাওয়ার খেয়ালই নেই। মুঠোফোনে মায়ের গলায় আদরমাখানো ‘ভাত খেয়েছিস?’ শুনতে কেমন লাগে? তখনকার মতো ‘জ্বালিও না তো’ বলে ঝাঁঝিয়ে উঠলেও এই বাক্যবন্ধের তলায় লুকনো স্নেহমায়ার ফল্গুধারাটি বাঙালির বড় প্রিয়। এ এক জাতিগত সংস্কৃতি, ঐতিহ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। চিরকেলে বাঙালির কাছে ‘পেটভরে খাওয়া’ বা ‘আরাম করে খাওয়া’র সমার্থক যেন ‘ভাত’। চাট্টি মাছভাত বা আলুভাতে-ডালভাত না হলে বাঙালির খাওয়ায় বুঝি তৃপ্তি হয় না। ‘খেয়েছ?’ এ প্রশ্নের মধ্যে অবধারিতভাবে কোথাও যেন লুকিয়ে থাকে ভাতের অনুষঙ্গ।
আসলে বাঙালি বরাবরই শস্যশ্যামলা নদীমাতৃক পলিমাটির মানুষ। সেখানে কবির কলমেও বারবার আসে চাল বা ধানের অনুষঙ্গ– কখনও ‘ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা’, কখনও বা ‘এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে’, আবার কখনও বা ‘শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে…’। বাঙালি পুজোপার্বণ থেকে লোকাচার, শুভ অনুষ্ঠান থেকে মৃত্যুপরবর্তী শাস্ত্রীয় আচার লক্ষ করলে দেখব, সবেতেই ভাত বা চাল অত্যাবশ্যক।
লক্ষ্মীপুজোয় চালের গুঁড়োর আলপনা, দরজায় গোড়ায় গোড়ায় ধানের শিষ, পুজোর পরে প্রসাদী চালকলামাখা থেকে শুরু করে ষোড়শোপচারে ঠাকুরের ভোগে খিচুড়ি, পোলাও এবং পায়েসের সদর্প উপস্থিতি, বিয়ের পরে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি যাবার কালে বাপের অন্নঋণ শোধ করার প্রথা কনকাঞ্জলি, শ্বশুরবাড়ির প্রথম আচার ‘বৌভাত’– ধান, চাল, ভাত ছাড়া বাঙালির এক পা চলবে না। পৈতে বা অশৌচের হবিষ্যান্নতেও সেই আলোচালের ভাত ফুটিয়ে খাওয়ার নিদান। মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তিকামনায় ভাত মেখে পিণ্ডদান, কিংবা কাককে ভাত খাওয়ানোতেও এই অন্নপ্রীতিরই নিদর্শন।
আরও পড়ুন: মন্দার মুখোপাধ্যায়ের কলমে: ঝাড়াঝুড়ি
বাঙালি শিশুরা একসময় যে ছড়া কেটে বড় হত, তাতেও খাওয়ার অনুষঙ্গে ভাতই প্রধান। সেই আদি মধ্যযুগের প্রাকৃত ভাষার ছড়া মনে করা যাক। কবি বলছেন– ‘ওগগরা ভত্তা, রম্ভৌ পত্তা, দুগ্ধ সযুক্তা, গাইকো ঘিত্তা, মোইলি মচ্ছা, নালিচ গচ্ছা, দিজ্জউ কন্তা, খা পুনবন্তা।’ অর্থাৎ কিনা যে গৃহস্বামীকে তাঁর স্ত্রী দুপুরে কলার পাতে ধোঁয়াওঠা ভাত (ওগগরা ভত্তা), দুধ, ঘি, মৈলি মাছের ঝোল, নালচে (পাট) শাকভাজা বেড়ে খেতে দেন, তিনিই প্রকৃতার্থে পুণ্যবাণ। ঈশ্বর গুপ্তের লেখাতেও পাই ‘ভাত মাছ খেয়ে বাঁচে বাঙালি সকল, / ধানে ভরা ভূমি তাই মাছে ভরা জল।’ আবার লোকায়ত ছড়াতেও রয়েছে, ‘দাদাভাই চালভাজা খাই, ময়না মাছের মুড়ো / হাজার টাকার বৌ এনেছি খাঁদা নাকের চুড়ো।’ কিংবা ‘আয়রে খোকন ঘরে আয় / দুধ মাখা ভাত বিড়ালে খায়।’ বাঙালির সই-পাতানোর খেলাতেও সেই ধান আর ভাতের গন্ধ – ‘কলম-কাঠির পাতলা চিঁড়ে, হামাই ধানের খই / চিনি-আতপ চালের পায়েস, খাবে এস সই।’
কাজেই বাঙালির ধানচাষের ইতিহাস খুঁড়তে গেলে অবধারিতভাবেই পিছিয়ে যেতে হবে কয়েক হাজার বছর। যখন প্রথম মানুষ শিখল লাঙল ধরতে, সেই থেকেই একটু একটু করে ধানের বীজের বিবর্তন হয়েছে ভারতের ভৌগোলিক সীমানা এবং ভূমিরূপ অনুযায়ী। মাটির রকমফেরের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এক বীজের সঙ্গে আর এক বীজের মিশেল দিয়ে নতুন রকম ধান্যবীজের উদ্ভাবন করে গিয়েছেন কৃষকরা, পুরুষানুক্রমে। ডারউইন যাকে তাত্ত্বিকভাবে বলেছেন ‘আর্টিফিশিয়াল সিলেকশন’, সেই পদ্ধতি মেনেই প্রাচীন যুগের কৃষকেরা তৈরি করেছেন ধানের নানারকম প্রকারভেদ। বর্তমানে কৃষিবিজ্ঞান বলে, পূর্বভারত ও বাংলাদেশে মূলত যে ধান চাষ হয়, তা ভাত রান্নার উপযুক্ত ‘ইন্ডিকা’ গ্রুপের চাল (বৈজ্ঞানিক নাম – ওরাইজ়া স্যাটাইভা)। এছাড়াও কিছু কিছু জলা জায়গায় ‘জাপোনিকা’ গ্রুপের ধানের চাষও দেখা যায়।

কৃষি ও ধানবিশেষজ্ঞ দেবল দেব-এর মতে, সবুজ বিপ্লবের আগে পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ মিলিয়ে ঠিক কত ধরনের ধান চাষ হত, তা এখন আর সঠিকভাবে জানার কোনও উপায়ই নেই। বৈজ্ঞানিকদের অনুমান, সংখ্যাটা পনেরো হাজারের কাছাকাছি। ষাটের দশক পর্যন্তও ভূমিরূপের পার্থক্য অনুযায়ী কৃষকেরা ধানের জিনগত বিভাজন ঘটিয়ে নতুন নতুন প্রকারভেদ সৃষ্টি করতেন। তার সংখ্যাও সাড়ে পাঁচ হাজারের কম হবে না। কিন্তু ১৯৬৫ সালের সবুজ বিপ্লবের পর, ছবিটা রাতারাতি পাল্টে গেল। কয়েক প্রকার উচ্চফলনশীল ধানের বীজের আবিষ্কার, হাজার হাজার স্থানীয় সনাতনী ধানের বীজকে বিলুপ্তির অন্ধকারে পাঠিয়ে দিল। বাংলাদেশেও সেই একই প্রক্রিয়ায় সত্তরের দশকে প্রায় সাত হাজার জিনবৈচিত্র-বিশিষ্ট ধানের বীজকে অস্তিত্বহীন করে দিয়ে চাষ করা হতে লাগল উচ্চফলনশীল ধান। পরবর্তী কয়েক দশকে ধানের বীজবৈচিত্র সাতশোতে নেমে এল বাংলাদেশের মতো উর্বর পললভূমিতে। কাজেই শেষ কথা হল এই যে, এইসব জিনবৈচিত্র বিশিষ্ট বীজ আজ কৃষি-সংগ্রহশালা ছাড়া আর বিশেষ কোথাও দেখা যায় না। চাষিদের হাতে তো নয়ই। দেবলবাবুর মতে, ২০১২ পর্যন্ত ৫৭৬ রকমের ধান চাষ করা হত দুই বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে। কিন্তু তার অধিকাংশই পরবর্তী বছরগুলোতে হারিয়ে গিয়েছে। অস্তিত্বহীন হয়ে গিয়েছে।
এই ক্ষতি যে শুধু বাংলার কৃষিক্ষেত্রে, তা ভাবলে ভুল হবে। প্রতিটি স্থানীয় ধান্যবৈচিত্রের সঙ্গে একটু একটু করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে স্থানীয় সংস্কৃতি ও লোকাচার। যেমন ধরা যাক কনকচূড় চালের কথা। সুগন্ধী এই চালের খই না হলে তৈরিই হবে না বাংলার ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি জয়নগরের মোয়া। মুড়ির চাল আর চিঁড়ের চাল যে আলাদা, সে কথা কি আপনি জানতেন? মুড়ির চালের অসংখ্য প্রকারভেদ রয়েছে দুই বাংলাতেই। ‘শালি ধানের চিঁড়ে’ আর ‘বিন্নি ধানের খই’ তো অমর হয়ে রয়েছে বাংলা ছড়াতেই। বাস্তবে কিন্তু এদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না।
বাংলাদেশের কৃষিবিজ্ঞানী শ্রাবন্তী রায়ের গবেষণা থেকে জানা যায় বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি, এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কেলাস, ডাহর-নাগরা, নলপাই আর মৌল ধানের চাষ হয়, যা থেকে মুড়ির উৎপাদন হয় সবচেয়ে বেশি। এছাড়া উত্তরবঙ্গের বিরই, তুলাইপাঞ্জি, কালো নুনিয়া আর নাগেশ্বরী – এই সুগন্ধী চালের তৈরি মুড়িও অত্যন্ত জনপ্রিয়।

বাংলাদেশে সবচেয়ে ভাল মুড়ি তৈরি হয় বরিশালে। সেখানকার লোকগানেই রয়েছে – ‘কচ্-কচা-কচকচ্-কচা-কচ্ ধান কাটিরে / (ও ভাই) ঝিঙ্গাশাইলের হুড়ুম ভালা / বাঁশফুলেরই ভাত / লাহি ধানের খইরে / দইয়ে তেলেসমাত… / কস্তুরগন্ধীর চাউলের আলা / সেই চাউলেরই পিঠা ভালা / সেই পিঠায় সাজিয়ে থালা / দাও কুটুমের হাতে রে।’ বলাই বাহুল্য এগুলির প্রতিটি দেশজ জাতের ধান থেকে তৈরি চাল এবং এখন এদের আবাদ প্রায়ই হয়ই না।
তবে বরিশালের অনেক জমিই আধুনিক উচ্চফলনশীল ধান চাষের উপযুক্ত নয়। ফলে কিছুটা বাধ্য হয়েই এখানে অনেক জাতের দেশজ ধানের চাষ এখনও টিঁকে আছে, যা থেকে খুব ভাল চিঁড়ে-মুড়ি-খই বানানো যায়। যেমন, নাখুচি, সাদা মোটা, নারকেল ঝোপা, সাদা পেকরাজ, পারমা, লালগাইচা, ঘিগজ, করচা মুড়ি, দুধরাজ, রঙ্গিখামা, আদুল জরা, লালহাইল, শংকরবটি প্রভৃতি ধান থেকে খুব ভাল মুড়ি হয়। পশ্চিম মেদিনীপুরের আজিরমান, চন্দ্রকান্তা আর মানিক কলমা থেকে খুব ভাল জাতের চিঁড়ে তৈরি হয়। তবে মেশিনে তৈরি উচ্চফলনশীল ধানের রমরমা বাজারে এসব ধান কতদিন চাষ করা যাবে, তা নিয়ে বিরাট প্রশ্নচিহ্ন থেকেই যাচ্ছে।
আর লোকাচারের কথা ধরলে তো চালকে বাদ দিয়ে এক পা চলার জো নেই। জৈষ্ঠে জামাইষষ্ঠী পালনে জামাইয়ের জন্যে রান্না হবে ফুরফুরে জুঁইফুলের মতো ভাত। জামাইনাড়ু, জামাইশাল চালের নামেই তার প্রকাশ। পুজোয় যে পায়েস রান্না হবে, সে চাল হতে হবে ছোট, সরু, সুগন্ধী। দেউলাভোগ, গোবিন্দভোগ, গোপালভোগ, বিষ্ণুভোগ, কার্তিকশাল, লক্ষ্মীচূড়া, লক্ষ্মীদীঘল, লক্ষ্মীজটা, ঠাকুরশাল, মোহনরাস, রাধাতিলক নামেই বোঝা যাচ্ছে, সে চাল সত্যিই দেবভোগ্য। কোন ধানের শিষের চেহারা কেমন, তা থেকেও নামকরণ হয়। যেমন, খেজুরছড়ি কিংবা নারকেলছড়ি ধানের শিষ সত্যিই খেজুরপাতা বা নারকেলপাতার মতো দেখতে।

কখনও পৌরাণিক চরিত্রের নামে নাম রাখা হয়েছে স্থানীয় দেশি চালের। যেমন, ভীমশাল, গৌরনিতাই, মেঘনাদশাল, রাবণশাল, সীতাশাল। এমনকী পোষা বা স্থানীয় জন্তুজানোয়ারের নামেও ধানের নাম রেখেছেন সেকালের কৃষকরা। হাতিধান, হাতিপাঁজর, হাঁসগুজি, হনুমানজটা, মুরগিশাল, শিয়ালভোমরা এসব নাম থেকেই স্থানীয় প্রাণিবৈচিত্রের খবর মেলে। কিন্তু এসব চালের কথা আর কিছুদিনের মধ্যেই কৃষি-ইতিহাসের ঝুরঝুরে হয়ে যাওয়া বইয়ের পাতায় ছাড়া আর কোথাওই পাওয়া যাবে না। ফলে এগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুজো, পার্বণ, ব্রত, আচার, অনুষ্ঠানগুলিও ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে থাকবে। তোষলা, পুণ্যিপুকুর, ইতুপুজো, ইঁদপুজো, নীলষষ্ঠীর মতো বারব্রতগুলির সঙ্গে একাত্ম হয়ে রয়েছে বাংলার ধান-চালের ইতিহাস ও সংস্কৃতি। এগুলিও আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে। জামাইষষ্ঠী হলেও জামাইশাল চালের সুগন্ধী ভাতের অভাবে ঐতিহ্যের গন্ধটা একেবারেই মিলিয়ে গেছে। লক্ষ্মীপুজোর পায়েসে লক্ষ্মীদীঘল চালের সুগন্ধ না পেয়ে লক্ষ্মীঠাকুরও মুখভার করেন।
স্থানীয় দেশজ চালের অভাবে কত ঐতিহ্যবাহী খাবার তাদের মূল স্বাদ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, সে খোঁজও রাখে না আত্মবিস্মৃত বাঙালি। বর্ধমানের যে সীতাভোগের খ্যাতি বিশ্ববিখ্যাত, তা একসময় তৈরি হত সীতাভোগ বা সীতাশাল নামের চাল থেকেই। সে চালের অবলুপ্তি ঘটেছে। সীতাভোগ এখন তৈরি হয় মেশিনে ছাঁটা উচ্চফলনশীল চাল থেকে। কাজেই সীতাভোগের আসল স্বাদ আপনি চাইলেও আর কোনওদিন পাবেন না। কনকচূড় চালের খই এখনও সামান্য পরিমাণে টিঁকে আছে ঠিকই। তবে কলের চালের ‘নকল’ জয়নগরের মোয়ার রমরমায় সে সুদিনও গেল বলে।

গ্রামবাংলায় খোড়ো চালের ঘর আর কটা দেখতে পান? কেন, কোনওদিন ভেবে দেখেছেন? কারণ লুকিয়ে সেই সনাতন দেশজ ধানের বীজের অবলুপ্তিতেই। আধুনিক উচ্চফলনশীল ধানের খড় ঘর ছাইবার উপযুক্তই নয়। আকারে ছোট, পাতলা এবং একেবারেই মজবুত নয়। ফলে পল্লীবাংলার যে চিরকেলে রূপটি কবিতায়, গানে, নাটকে, নভেলে ধরা রয়েছে, সে রূপের আর দেখা মেলে না।
সৌজন্যে? না। কেবল টেলিভিশনের গ্রাস নয়, মোবাইলের ত্রাসও নয়। কারণটি লুকিয়ে দেশজ শস্যের অবমাননায়, অবহেলায়। বিশ্বব্যাপী বাঙালি যে জাত্যাভিমান, যে ঐতিহ্য, যে সংস্কৃতি নিয়ে অবলীলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা খরচ করে, জানতেও পারে না, স্থানীয় শস্যের জিনগত অবলুপ্তিতে কীভাবে সেসব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বারব্রত থেকে পুজোপার্বণ তো বটেই, ক্রমশ বাংলা ভাষা থেকেও হারিয়ে যাবে পুরনো চাল ভাতে বাড়ে, বারেবারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, মাছে-ভাতে বাঙালি— এইসব প্রবাদ-প্রবচনগুলি। এভাবেই প্রতিবার একটি করে দেশজ ধানের জিনগত প্রকারভেদের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে হারিয়ে যাবে বাঙালির নিজস্বতা, স্বাতন্ত্র্য, সংস্কৃতি ও লোকায়ত প্রথাগুলি।৫
তথ্যঋণ –
ডাঃ দেবল দেব, স্ক্রোল ডট ইন, মার্চ ২০২১
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকা, জুলাই ২০১৮
শ্রাবস্তী পি রায়, গ্রিন বাংলা, ২০১৭
মৃত্যুঞ্জয় রায়, কৃষিকথা পত্রিকা, জৈষ্ঠ্য ১৪২৬
লিখতে শিখেই লুক থ্রু! লিখতে লিখতেই বড় হওয়া। লিখতে লিখতেই বুড়ো। গান ভালবেসে গান আর ত্বকের যত্ন মোটে নিতে পারেন না। আলুভাতে আর ডেভিলড ক্র্যাব বাঁচার রসদ। বাংলা বই, বাংলা গান আর মিঠাপাত্তি পান ছাড়া জীবন আলুনিসম বোধ হয়। ঝর্ণাকলম, ফ্রিজ ম্যাগনেট আর বেডস্যুইচ – এ তিনের লোভ ভয়ঙ্কর!!








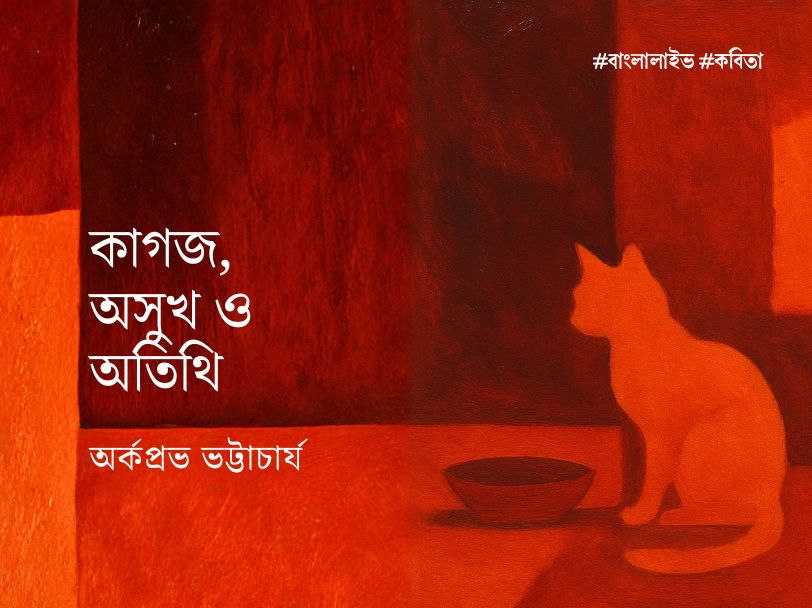


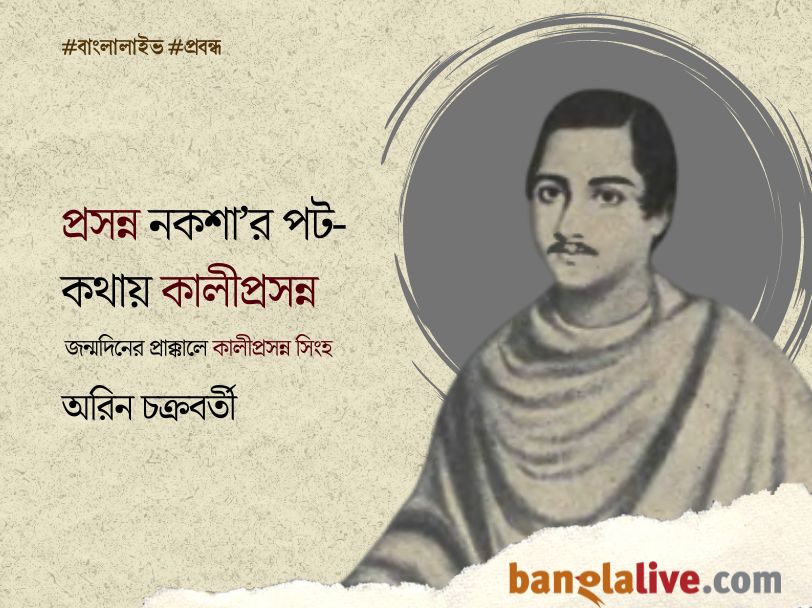




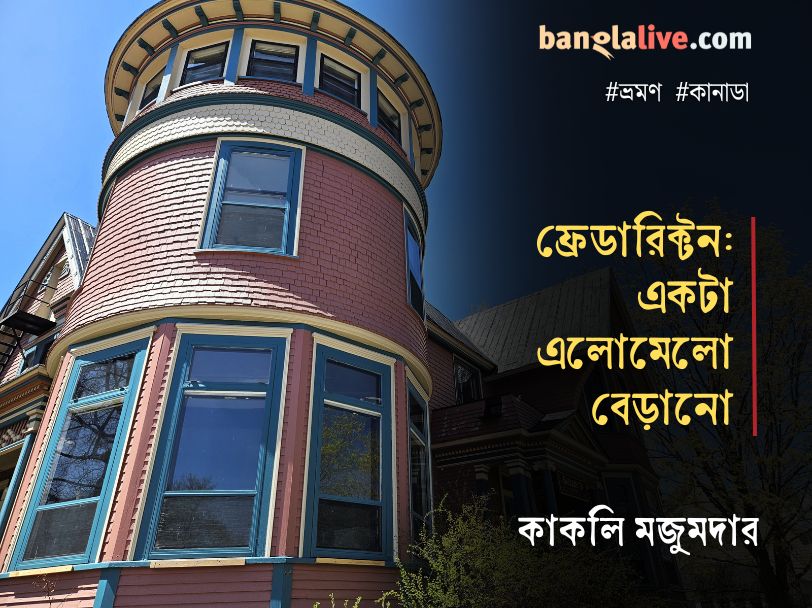
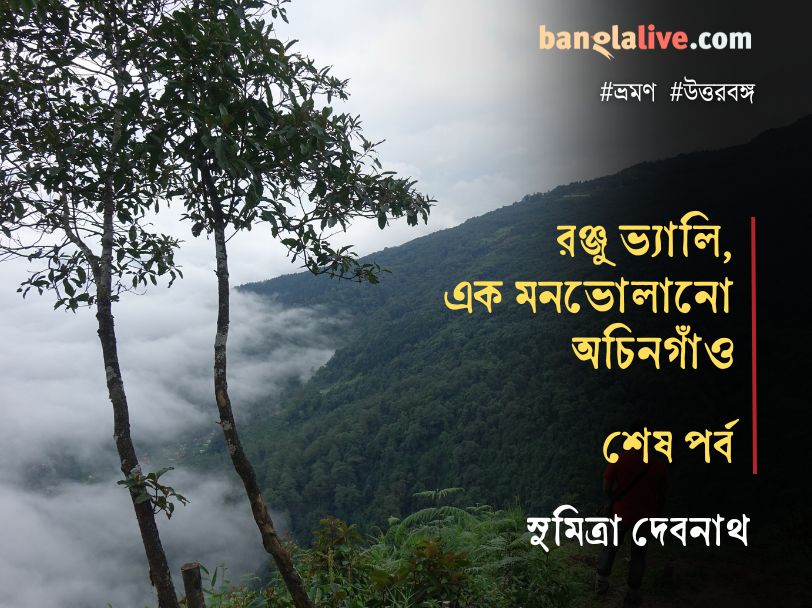








One Response
তথ্য সংকলন প্রশংসনীয়। বাদ পড়েছে ‘কোমল চাল’, যা সেদ্ধ করতে হয় না।