বেড়াল না রুমাল ? আলো কে? তার স্বভাব কেমন? মানুষ নিশ্চয়ই এমন একটা প্রশ্নের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সৃষ্টির আদিকাল থেকেই। ফরাসি গণিতজ্ঞ-দার্শনিক দেকার্ত সপ্তদশ শতকে আলোর ধর্মগুলির একটা তালিকা বানিয়েছিলেন- যেমন, যে কোনও আলোকিত বস্তু থেকে আলো সমস্ত দিকে বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ে, আলো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তৎক্ষণাৎ চলে যেতে পারে (অর্থাৎ আলোর গতিবেগ অসীম), আলো সচরাচর সরলরেখায় চলে, ইত্যাদি। ১৭০০ সাল নাগাদ স্যর আইজাক নিউটন ধারণা করেন, আলো আসলে একধরনের কণার সমষ্টি, যা কোনও উৎস থেকে রওনা হয়ে অবিশ্রাম ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। আলো যে সরলরেখায় চলে, বা আলোর প্রতিফলন (reflection) ও প্রতিসরণ (refraction)-এর সূত্র, সবই দেখা গেল দিব্যি বোঝানো যাচ্ছে এই কণা-মডেল দিয়ে। মনে হল যাক, তাহলে তো আলোর রহস্যভেদ হয়েই গেল।“Whence arises all that order and beauty we see in the world?”
-স্যর আইজাক নিউটন, “অপটিক্স”
[the_ad id=”270088″]
মুশকিল হল, আলোকের অন্য কিছু ধর্ম, যেমন বিচ্ছুরণ (diffraction), ব্যতিচার (interference) ইত্যাদি দেখা গেল এই ছবি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। বস্তুত, নিউটনেরই প্রায় সমসাময়িক ইতালীয় বিজ্ঞানী গ্রিমালদি ও ডাচ বিজ্ঞানী হাইগেনস আলোকে বলেছিলেন “ঢেউয়ের মতো”। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী টমাস ইয়ং একটি পরীক্ষার কথা বলেন, যেখানে দুটো ছিদ্র থেকে আসা আলোকরশ্মিগুলিকে একে অন্যের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেওয়া হচ্ছে আর তারা আলোছায়ার একটা নকশি ঝালর তৈরি করছে। জলের ঢেউ একে অন্যের ওপর এসে পড়লে যেমন আলপনা সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে আরেকটা চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে গেল। ড্যানিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ওলে রোয়েমার বৃহস্পতির চাঁদের গ্রহণের সময়কাল থেকে অঙ্ক কষে আলোর গতিবেগ বের করে ফেললেন। দেখা গেল, আলোর গতিবেগ অসীম নয় মোটেই, তার মান সেকেন্ডে প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার (রোয়েমার তাঁর হিসেবে পেয়েছিলেন আরেকটু কম)।
এই গতিবেগ কতটা? আমরা যদি পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের কথা ভাবি, ওই বিশাল পথ অতিক্রম করতে আলোর লাগবে মাত্র এক সেকেন্ডের চেয়ে সামান্য বেশি সময়। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় তাই এই গতিবেগকে অসীম বলে মনে হবে, যেমনটি ভেবেছিলেন দেকার্ত।
ইতিমধ্যে আরেকটা চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে গেল। ড্যানিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ওলে রোয়েমার বৃহস্পতির চাঁদের গ্রহণের সময়কাল থেকে অঙ্ক কষে আলোর গতিবেগ বের করে ফেললেন। দেখা গেল, আলোর গতিবেগ অসীম নয় মোটেই, তার মান সেকেন্ডে প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার (রোয়েমার তাঁর হিসেবে পেয়েছিলেন আরেকটু কম)।
এই গতিবেগ কতটা? আমরা যদি পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের কথা ভাবি, ওই বিশাল পথ অতিক্রম করতে আলোর লাগবে মাত্র এক সেকেন্ডের চেয়ে সামান্য বেশি সময়। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় তাই এই গতিবেগকে অসীম বলে মনে হবে, যেমনটি ভেবেছিলেন দেকার্ত।
বিশ শতকের শুরুতে কিন্তু কণিকাতত্ত্ব আবার ফিরে এল মহাসমারোহে। ধাতব তলের ওপর আলো ফেললে দেখা যাচ্ছিল, ইলেকট্রন নির্গত হয়, তারই পোশাকি নাম ফোটো-ইলেক্ট্রিক এফেক্ট। এই ঘটনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আইনস্টাইন বললেন, আলো আসলে কতগুলো “এনার্জি প্যাকেট”-এর সমাহার। মানে, এনার্জি বা শক্তি দিয়ে গঠিত ছোট্ট ছোট্ট পোঁটলা —তারা ধাতু থেকে ইলেকট্রনকে উৎখাত করে বাইরে বের করে আনছে। আইনস্টাইন এই প্যাকেটগুলোকে বললেন “লাইট-কোয়ান্টাম”, পরে আস্তে আস্তে তারা পরিচিত হতে শুরু করল “ফোটন” নামে।যাই হোক, এরপর আস্তে আস্তে আলোর তরঙ্গধর্মই বেশি চর্চিত হতে থাকল। উনিশ শতকে জেমস ম্যাক্সওয়েল তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের তত্ত্ব দিলেন, দেখা গেল আলোর যা গতিবেগ, অড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের বেগও ঠিক ততটাই। বোঝা গেল, আলো তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ পরিবারেরই একজন। আলোর তরঙ্গ-অস্তিত্ব নিয়ে কোনও সংশয় রইল না আর। বিশ শতকের শুরুতে কিন্তু কণিকাতত্ত্ব আবার ফিরে এল মহাসমারোহে। ধাতব তলের ওপর আলো ফেললে দেখা যাচ্ছিল, ইলেকট্রন নির্গত হয়, তারই পোশাকি নাম ফোটো-ইলেক্ট্রিক এফেক্ট। এই ঘটনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আইনস্টাইন বললেন, আলো আসলে কতগুলো “এনার্জি প্যাকেট”-এর সমাহার। মানে, এনার্জি বা শক্তি দিয়ে গঠিত ছোট্ট ছোট্ট পোঁটলা — তারা ধাতু থেকে ইলেকট্রনকে উৎখাত করে বাইরে বের করে আনছে। আইনস্টাইন এই প্যাকেটগুলোকে বললেন “লাইট-কোয়ান্টাম”, পরে আস্তে আস্তে তারা পরিচিত হতে শুরু করল “ফোটন” নামে। প্রসঙ্গত, এই লাইট কোয়ান্টামদের গণনাপদ্ধতি নিয়ে যুগান্তকারী কাজ করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। সেই কাজ তিনি গবেষণাপত্রের আকারে লিখে পাঠান আইনস্টাইনকে, আইনস্টাইন স্বয়ং তার জার্মান অনুবাদ করে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামে ছাপানোর ব্যবস্থা করেন।
[the_ad id=”270086″]
অর্থাৎ, বোঝা গেল, আলোকে তরঙ্গের মতোও ভাবা যায়, আবার কণিকার মতোও। যেন হ য ব র ল -র সেই বেড়াল, যাকে কখনও দেখা যায় রুমাল হিসেবে, কখনও বেড়াল। রং দিয়ে যায় চেনা সাদা আলো যে আসলে অজস্র রঙের সমাহার, সে তো আমরা জানিই। প্রিজমের মধ্যে দিয়ে গেলে সেই বর্ণালী বিশ্লিষ্ট হয়ে আলাদা আলাদা রং দেখায়। আলোর তরঙ্গধর্মের কথা বলছিলাম না আমরা? ঢেউয়ের তো একটা শীর্ষ থাকে, থাকে একটা নিম্নতম বিন্দুও। পাশাপাশি অমন দুটো শীর্ষর মধ্যে যে দূরত্ব, তা-ই হল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য। আর আলাদা রঙের আলো মানে আর কিছুই নয়, এই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের প্রকারভেদ। যেমন, লাল আলোয় ঢেউয়ের দুটো চূড়ার মধ্যে যা দূরত্ব, নীল আলোয় তার চেয়ে অনেক কম। কোয়ান্টাম মেকানিক্স বলে, পদার্থের মধ্যে ইলেকট্রন থাকে কতগুলো নির্দিষ্ট শক্তিস্তরে (energy level)। এবার, ধরা যাক উঁচুতে থাকা শক্তিস্তর থেকে একটা ইলেকট্রন টপ করে নেমে পড়ল নীচের শক্তিস্তরে। এর জন্য তাকে কিছু শক্তি খসাতে হল (নইলে নীচের স্তরে তার ঠাঁই হবে কেন!), সেটা আর একটা ফোটনের আকারে বেরিয়ে এল। এই ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট, অতএব একটি নির্দিষ্ট রঙের আলোর রেখা তৈরি হয়। বস্তুত, যে আলোই আমরা দেখি না কেন, তার উৎস কিন্তু এমনই কোনও ইলেকট্রনের “আপার বার্থ” থেকে “লোয়ার বার্থ”-এ নেমে আসা। নিচু থেকে উঁচু শক্তিস্তরে ইলেকট্রন যাওয়ার সময়ে উল্টোটা ঘটে — তাকে একটা ফোটন বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে হয়। প্রথম ক্ষেত্রে সাদা পাতায় রঙিন দাগ, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রঙিন পাতায় কালো দাগের মত বর্ণালী দেখা যায়। প্রথমটির নাম নির্গমন বর্ণালী, দ্বিতীয়টির নাম শোষণ বর্ণালী। এখন, প্রত্যেকটা মৌলের ভিতরের শক্তিস্তরের বিন্যাস তো আলাদা আলাদা — তাই এই বর্ণালীরেখাদের (spectral lines) রঙও আলাদা আলাদা হয়। তাই বর্ণালীরেখা হল প্রত্যেকটি মৌলকে সনাক্ত করার এক নির্ভুল পদ্ধতি। অর্থাৎ, বর্ণালীরেখায় কার কানের কাছে নীল চামড়া আর কার মাথার ওপরের লাল কালির ছাপ, তা দেখেই বলে দেওয়া সম্ভব, পদার্থটি হাইড্রোজেন না হিলিয়াম না সোডিয়াম না অন্য কিছু।
কোয়ান্টাম মেকানিক্স বলে, পদার্থের মধ্যে ইলেকট্রন থাকে কতগুলো নির্দিষ্ট শক্তিস্তরে (energy level)। এবার, ধরা যাক উঁচুতে থাকা শক্তিস্তর থেকে একটা ইলেকট্রন টপ করে নেমে পড়ল নীচের শক্তিস্তরে। এর জন্য তাকে কিছু শক্তি খসাতে হল (নইলে নীচের স্তরে তার ঠাঁই হবে কেন!), সেটা আর একটা ফোটনের আকারে বেরিয়ে এল। এই ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট, অতএব একটি নির্দিষ্ট রঙের আলোর রেখা তৈরি হয়। বস্তুত, যে আলোই আমরা দেখি না কেন, তার উৎস কিন্তু এমনই কোনও ইলেকট্রনের “আপার বার্থ” থেকে “লোয়ার বার্থ”-এ নেমে আসা। নিচু থেকে উঁচু শক্তিস্তরে ইলেকট্রন যাওয়ার সময়ে উল্টোটা ঘটে — তাকে একটা ফোটন বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে হয়। প্রথম ক্ষেত্রে সাদা পাতায় রঙিন দাগ, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রঙিন পাতায় কালো দাগের মত বর্ণালী দেখা যায়। প্রথমটির নাম নির্গমন বর্ণালী, দ্বিতীয়টির নাম শোষণ বর্ণালী। এখন, প্রত্যেকটা মৌলের ভিতরের শক্তিস্তরের বিন্যাস তো আলাদা আলাদা — তাই এই বর্ণালীরেখাদের (spectral lines) রঙও আলাদা আলাদা হয়। তাই বর্ণালীরেখা হল প্রত্যেকটি মৌলকে সনাক্ত করার এক নির্ভুল পদ্ধতি। অর্থাৎ, বর্ণালীরেখায় কার কানের কাছে নীল চামড়া আর কার মাথার ওপরের লাল কালির ছাপ, তা দেখেই বলে দেওয়া সম্ভব, পদার্থটি হাইড্রোজেন না হিলিয়াম না সোডিয়াম না অন্য কিছু।
[the_ad id=”270085″]
উনিশ শতকের শেষ দিকে জুল জ্যানসেন নামে এক ফরাসি বিজ্ঞানী ভারতে এসে সূর্যগ্রহণের সময়ে বর্ণালী বিশ্লেষণ করেন। সেখানে দেখা গেল, একটা তীব্র হলুদ দাগ। কাছাকাছি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দুটো হলুদ রেখা তখন সোডিয়ামের টিপসই হিসেবে স্বীকৃত — কিন্তু এই নতুন দাগটি তার চেয়ে আলাদা। হিলিয়ামকে প্রথম চিহ্নিত করা গিয়েছিল এভাবেই, ওই মৌলটির অস্তিত্ব তার আগে জানাই ছিল না কারও। আলোই তবে প্রথম সন্ধান দিল, এক নতুন পদার্থের? আর হ্যাঁ, এই প্রসঙ্গে আরও এক বাঙালি বিজ্ঞানীর কথা বলতেই হয়। মেঘনাদ সাহা । নক্ষত্রের শোষণ বর্ণালী থেকে তার তাপমাত্রা ও অন্যান্য ভৌত অবস্থা কীভাবে আন্দাজ করা যেতে পারে, সেই গবেষণার পথিকৃৎ ছিলেন তিনি। আধুনিক জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যায় “সাহা আয়োনাইজেশন ইকুয়েশন”-এর গুরুত্ব অপরিসীম। এক শক্তিস্তর থেকে আরেক শক্তিস্তরে ইলেক্ট্রনের যাতায়াতের কথা হচ্ছিল। এখানে লেজাররশ্মির কথাও অল্প বলা যাক। LASER পুরো কথাটা হল Light Amplification by Simulated Emission of Radiation। লেজারে বহিরাগত একটি আলোককণিকা ফোটনের অভিঘাতে উঁচুতে থাকা শক্তিস্তর থেকে একটা ইলেকট্রন নীচের স্তরে নেমে আসে ফোটন খসিয়ে, যেটা অবিকল ওই আগের ফোটনটার মতো।উনিশ শতকের শেষ দিকে জুল জ্যানসেন নামে এক ফরাসি বিজ্ঞানী ভারতে এসে সূর্যগ্রহণের সময়ে বর্ণালী বিশ্লেষণ করেন। সেখানে দেখা গেল, একটা তীব্র হলুদ দাগ। কাছাকাছি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দুটো হলুদ রেখা তখন সোডিয়ামের টিপসই হিসেবে স্বীকৃত — কিন্তু এই নতুন দাগটি তার চেয়ে আলাদা। হিলিয়ামকে প্রথম চিহ্নিত করা গিয়েছিল এভাবেই, ওই মৌলটির অস্তিত্ব তার আগে জানাই ছিল না কারও।তাহলে সাধারণ আলোর সঙ্গে লেজার লাইটের তফাৎ কোথায়? আলো যে একরকম ঢেউ, সেই ছবিটায় ফিরে যাই। সাধারণ আলোর ক্ষেত্রে পর পর আসা ঢেউ গুলো অবিন্যস্ত — একটার শীর্ষ হয়তো আর একটার নিম্নবিন্দুতে পড়েছে, আর একটার শীর্ষ মাঝখানে, এরকম — অর্থাৎ তাদের “দশা” ( phase) আলাদা আলাদা। ঢেউয়েদের তরঙ্গদৈর্ঘ্যও পৃথক। উল্টোদিকে, লেজারে প্রত্যেকটা ঢেউ সুশৃঙ্খল। সবার শীর্ষ একজায়গায় , নিম্নবিন্দু একজায়গায়। বিজ্ঞানের পরিভাষায় এর নাম “কোহেরেন্স”। এই ঢেউদের সব্বার তরঙ্গদৈর্ঘ্যও সমান। অর্থাৎ, এমনি আলো যদি হয় গড়িয়াহাটের বাজারে লোকজনের এলোমেলো যাতায়াত, ঠেলাঠেলি, লেজার হল রাজপথে সেনাবাহিনীর সম্মিলিত নিখুঁত কুচকাওয়াজ। তাই লেজারের তীব্রতা, ক্ষমতা অনেক বেশি। বিজ্ঞান থেকে যন্ত্রশিল্প, প্রতিরক্ষা থেকে চিকিৎসাশাস্ত্র, সর্বত্রই আজ এই লেজাররশ্মির একাধিপত্য।
[the_ad id=”270084″]
অন্ধকারের উৎস হতে আলো সম্পর্কে প্রচলিত কত ধারণাই তো আমাদের পাল্টাতে হয়েছে। আলো কেবলমাত্র সরলরেখায় চলে এমনই ভাবা হত, কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল মহাকর্ষের প্রভাবে আলোও বাঁক নেয়। আবার, মহাজগৎ সম্পর্কে আমাদের পুরনো অনেক ধারণাও পাল্টে দিয়েছে আলোকবর্ণালী। কীভাবে? এই যে বলছিলাম বর্ণালীরেখাগুলো হল প্রত্যেকটি মৌলের নিখুঁতভাবে শনাক্ত করার উপায়, এখানে কিন্তু ধরেই নেওয়া যে, যার বর্ণালীর কথা হচ্ছে আর যে সেটা দেখছে, তারা একে অন্যের সাপেক্ষে স্থির। কিন্তু যদি তাদের গতিবেগ আলাদা হয়? মহাবিশ্বে তো সবকিছুই চলমান![the_ad id=”266919″]
একটা তারা যদি আমাদের থেকে দূরে সরে যেতে থাকে, তার বর্ণালীদাগের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি দেখায়, আর একটা তারা যদি আমাদের কাছে এগিয়ে আসতে থাকে, তার বর্ণালীদাগের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম দেখায়। প্রথমটাকে বলে “রেড শিফট”, দ্বিতীয়টাকে “ব্লু শিফট” (ওই যে বলছিলাম, দুটো নীল ঢেউয়ের শীর্ষবিন্দুরা বেশি কাছাকাছি, লাল ঢেউয়ের শীর্ষবিন্দুরা দূরে দূরে!)। এর কারণ ডপলার এফেক্ট — সেই যেমন কাছে আসতে থাকা ট্রেনের হুইসল বেশি তীক্ষ্ণ (অর্থাৎ তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম, কম্পাঙ্ক বেশি) শোনায়, আর দূরে চলে যেতে থাকা ট্রেনের হুইসল কম তীক্ষ্ণ (তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি, কম্পাঙ্ক কম) শোনায়।[the_ad id=”270084″]
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ম্যাপ খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। কোনও তারা কোনদিকে সরে যাচ্ছে, তার হদিশ অভ্রান্তভাবে খুঁজে পাওয়া যায় আলোর এই “রেড শিফট” কিংবা “ব্লু শিফট” দেখে। অনেক দূরের গ্যালাক্সির দিকে এভাবে তাকানো যায় যদি, দেখা যায় সবাই আসলে দূরে দূরে সরে যাচ্ছে। যে-যত দূরে, সরে যাবার তাড়া তার তত বেশি। এই মহাবিশ্ব যে আসলে প্রসারণশীল, গ্রহ তারা সবাই যে আসলে সবার থেকে দূরে চলে যাচ্ছে ক্রমাগত, তা তো এই আলোর খেলা দেখে বোঝাই যায়। এমনকী, সব কিছু যে আদতে একটি বিন্দু থেকে শুরু হয়েছিল, সেই বিগ ব্যাং-এর ধারণাও কিন্তু এ থেকে চলে আসে। আলোর চেয়ে বড় ইতিহাসলেখক, আলোর চেয়ে বড় ভবিষ্যৎবেত্তা তবে আর কে!পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনা আর গবেষণায় নিযুক্ত। লেখালেখির হাতেখড়ি ছোটবেলায়, সন্দেশ পত্রিকায়। প্রকাশিত কবিতার বই পাঁচটি, জার্নালধর্মী ভ্রমণকথার বই একটি। ভারতের সাহিত্য অকাদেমি যুব পুরস্কারে সম্মানিত। এছাড়াও পেয়েছেন কৃত্তিবাস পুরস্কার, বাংলা আকাদেমি পুরস্কার, এবেলা অজেয় সম্মান।






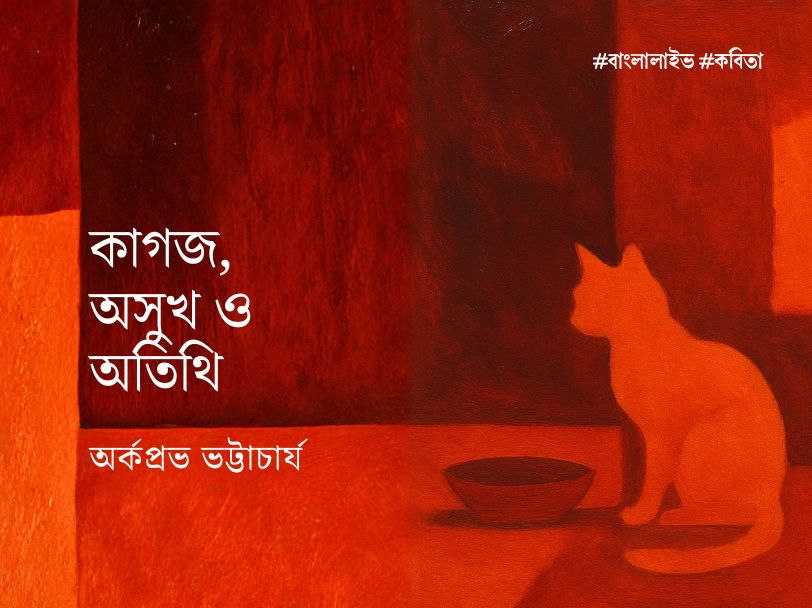


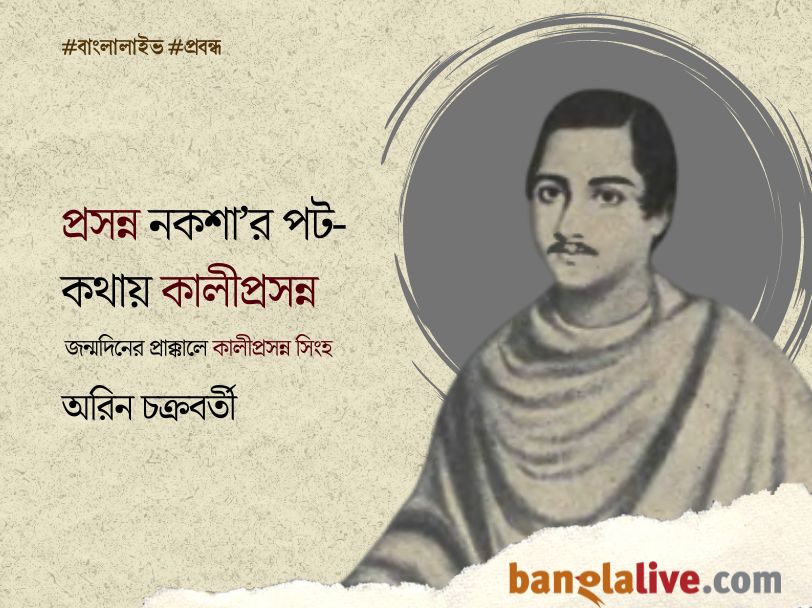




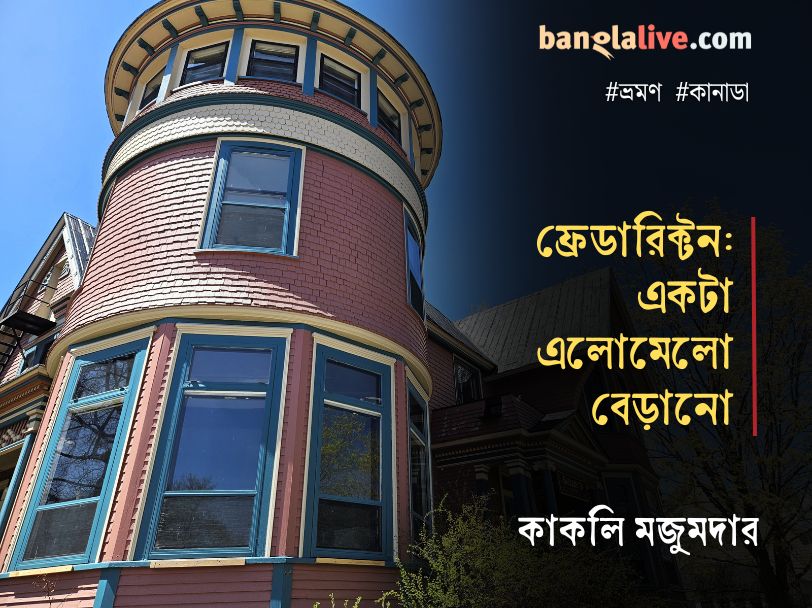
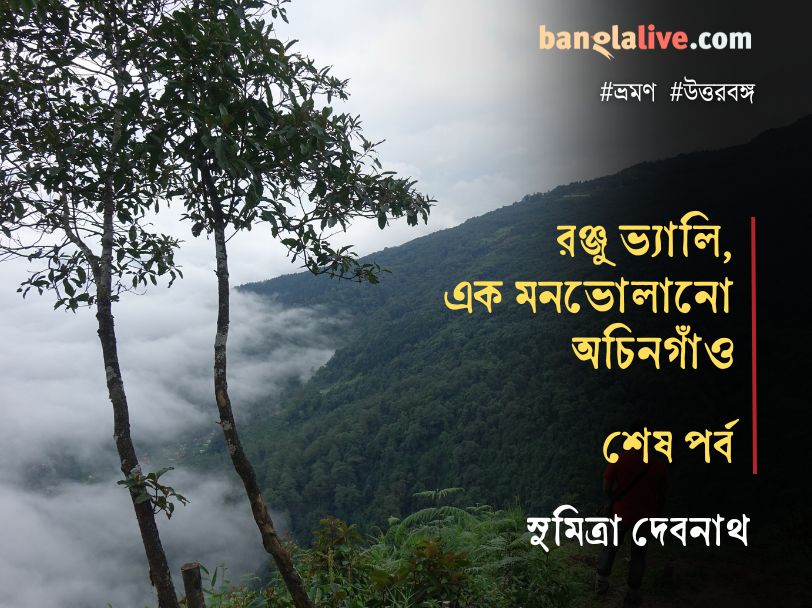








One Response
বাংলা ভাষায় এমন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়তে পারা সৌভাগ্যের বিষয়। এমন প্রবন্ধ আরো লেখা হোক।