ঠিক কবে যে মুখে মুখে কবিতা বলা থেকে আমি নিজে হাতে লেখায় উন্নীত হলাম, তা এখন আর মনে নেই। কারণ আমার তো হাতেখড়ি বলে কিছু হয়নি। আমাদের বাড়িতে অনুষ্ঠানের বহর এমনিতেই কম। জন্মদিনও করা হত না। মা বলতেন, এই সব অনুষ্ঠান ছোটদের আহ্লাদ দিয়ে মাথায় তোলার সামিল। এতে ছেলেমেয়ের বিগড়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। সারা জীবনই মা কেবল অ্যাবসোলিউট নয়, ব্রুট মেজরিটি উপভোগ করে এসেছেন সংসারে। তাঁর বিরোধীপক্ষ বলে কেউ ছিল না। তবে আমি শৈশবেই বুঝতাম, একজনের উপার্জনে পাঁচজনের সংসার সুন্দর ভাবে চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কান্ডারি মা নিজের মতো করে কিছু ব্যয় সংকোচ করতেন। কোন খরচগুলি অনাবশ্যক, সে বিষয়ে অন্য কারও মতামত নিতেন না। বাবারও নয়।
অন্নপ্রাশনের ভাত মুখে দেবার আগে শিশুর সামনে রাখা হত, টাকা, মাটির ঢেলা ও ঝরনা কলম। এর মধ্যে কলমটি সবচেয়ে রংচঙে। কাজেই আমরা তিন ভাইবোনই কলম ধরেছি। এতেই মা যারপরনাই খুশি। অতএব আবার হাতেখড়ির দরকার কী?
[the_ad id=”266918″]
যতদূর মনে পড়ে, আমার থেকে ছ’বছরের বড় বড়দা উদ্যোগী হয়ে অক্ষর লিখিয়েছিল। তখন আমার বয়স নিশ্চয়ই পাঁচ পেরিয়ে গেছে। কারণ সাড়ে ছ’বছর বয়সে আমি স্কুলেই ভর্তি হয়ে গেছি, একটু বেলা করে, সোজা ক্লাস টু-তে। স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগের পর্বে, আমাকে বাবা এনে দিতেন ছোট ছোট লাইন টানা ডায়রি আর পেনসিল। একটি করে ছোট ডায়রি কবিতায় ভরে উঠলেই আর একটি। মোড়ের মাথার মনোহারী দোকানে ডায়রি, পেনসিল সবই পাওয়া যেত। কয়েক বছর পর নিজের কবিতার ডায়রি নিজেই কিনে আনতাম। লিখতে শেখা ও স্কুলে ভর্তি হবার আগের সময়টা বেশ আনন্দে কেটেছিল। বাড়ির পাশের হাজরা পার্কে আগে থেকেই খেলতে যাই, একাই। এটাতে ভয়ের বা চিন্তার কিছু আছে, কেউ মনে করতেন না। আমার মতো বড়দাও কখনও সখনও যেত পার্কে। আমাদের দেখা হয়ে যেত ঘুরতে ঘুরতে। ছোড়দা খেলতে যেত হরিশ মুখার্জি মোড়ের উল্টো দিকের ফরোয়ার্ড ক্লাবে। ক্লাবটা ততদিন ছিল, যতদিন হরিশ মুখার্জি রোড সোজা এগিয়ে গিয়ে মাঠটাকে খেয়ে নেয়নি।
অন্নপ্রাশনের ভাত মুখে দেবার আগে শিশুর সামনে রাখা হত, টাকা, মাটির ঢেলা ও ঝরনা কলম। এর মধ্যে কলমটি সবচেয়ে রংচঙে। কাজেই আমরা তিন ভাইবোনই কলম ধরেছি। এতেই মা যারপরনাই খুশি। অতএব আবার হাতেখড়ির দরকার কী?
হাজরা পার্কে আমার খেলতে যাওয়ার ব্যাপারটা ছিল একটা মিথ, কারণ আমি তো খেলতাম না। আমার কোনও বন্ধু ছিল না। খুব শীর্ণ ছিলাম, চোখে চশমা উঠেছিল অনেক ছোটবেলায়। সেই চশমা পাছে ভাঙে, তাই সদা সংকুচিত হয়ে থাকতাম। চু কিতকিত বা গোল্লাছুটের দলগুলি আমাকে খেলায় নিত না। নিলেও আমাকে এলেবেলে করে রাখত আমার অগোচরেই। আর দুষ্টু, গুন্ডা প্রকৃতির কিছু ছেলের দলকে আমি এড়িয়ে চলতাম নিজেই।
[the_ad id=”266919″]
ডায়রি-পেনসিল পাওয়ার পর আমার একটু গুরুত্ব বৃদ্ধি হল নিজের কাছেই। পার্কের সামনের দিকেই গাছ গাছালির আড়ালে পাথরের যে বেদি ছিল, সেখানে বসে কবিতা লিখতাম। ওখানে ছিল ঝাউ-জাতীয় বড় কিছু গাছ, প্রচুর ঘৃতকুমারী ও ফণিমনসার জঙ্গল। একটা পাতাহীন গাছ ছিল। তার আঙুলের মতো নরম ডাল ভেঙে নিলে দুধের মত আঠা গড়াত। আমি ভাবতাম গাছটার রক্তের রঙ সাদা। ওই জঙ্গলের মাথায় বিকেলের দিকে অনেক ফড়িং উড়ত, তাদের স্বচ্ছ নীলচে পাখার মধ্যে দিয়ে আকাশ দেখা যেত। ছোটদের মধ্যেও নিষ্ঠুরতা থাকে, যদি তারা মানুষকে একমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণী জেনে বড় হয়। ওদের পায়ে সুতো বেঁধে ওড়াবার খেলা আমি সহ্য করতে পারতাম না। তবে আমিও অল্পসময়ের জন্য ফড়িং ধরে উড়িয়ে দিয়েছি। তারা আমার ছোট দুই আঙুলের মধ্যে ধড়ফড় করত, সেই ভয়ের কাঁপন আমার মনেও ভয় জাগাত, মৃত্যুর।

কবিতার খাতাটা এমনভাবে বুকের কাছে ধরা থাকত যে, বড় ছোট যে কেউ জানতে চাইবে, ওটা কী? তখন আমি বিজ্ঞের মতো বলব, জানো আমি কবিতা লিখি এতে। আর এটাও বলতে ভুলব না যে বড় হয়ে আমি লেখক হব। বিশাল মনে হত পার্কটাকে তখন, রঙ্গনের বেড়ায় ঘেরা তার ঘাসজমি, ভাগ ভাগ করা খেলার জন্য। কোথাও ফুলের কেয়ারি, কোথাও জল ধরার জন্য সিমেন্টের বাহারি জলাধার। মাঝখানে একটা বাহারি ফোয়ারা, তার জল ওপরের ধাপ থেকে উপচে নীচে, আরও নীচে চলে আসে। অথচ একফোঁটাও নীচের ঘাসজমিতে পড়ে না। তাকিয়ে দেখতে থাকি দু’চোখ ভরে আর বিস্ময় কাটে না। পার্কের পরিসীমায় ছিল একটা পিচরাস্তা। যেদিন খেলায় ‘এলেবেলে’ হতাম না, সেদিন ওই রাস্তা ধরে হাঁটতাম, আপন মনে কথা বলতাম, গাছেদেরও নানা প্রশ্ন করতাম। তাদের পাতায় জমা ধুলো মুছতে মুছতে আমার হাতের আঙুল কালো হয়ে যেত। বাড়িতে মা বুঝতে পারত কিনা জানি না, কারণ ফেরার আগে মালিদের ঘরের কল থেকে হাত-পা ধুয়ে নিতাম। এখন বুঝি, আমার কবিসত্বার বিকাশে কলকাতা করপোরেশনের ওই পার্কটির এক বড় ভূমিকা ছিল। তার রাঙা করবী ফুলে ভরা গাছ, মাটিতে ঝরে থাকা অজস্র কলকে ও বকুলের ফুল, মালিদের বাগানে ফোটানো অজস্র ডালিয়া কিংবা সূর্যমুখীর বর্ণবিন্যাস আমার মনকে এমন আনন্দে ভরে রাখত, যে একাকিত্বের বোধ জাগতেই পারত না।
[the_ad id=”270084″]
ওখানেই পড়েছিলাম জীবনের অন্যতম প্রথম কবিতা, যা বইয়ের পাতায় নয়, পাথরে খোদাই করা ছিল। হাজরা পার্কের পোশাকি নাম ছিল যতীন দাস পার্ক। সে নাম অবশ্য বড় একটা কেউ ব্যবহার করত না। তবে পার্কের একধারে, রাস্তার দিকে মুখ করে, যতীন দাসের আবক্ষ মর্মর মূর্তি ছিল। তার পাথরের থামের একদিকে খোদাই করা ছিল, “উদয়ের পথে শুনি কার বাণী, ভয় নাই ওরে ভয় নাই। নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।”
প্রায় প্রতিদিনই আমি লোহার রেলিং-ঘেরা ওই মূর্তির নিভৃত কুঞ্জে ঢুকতাম গেটের নীচের সরু ফাঁক গলে। চারপাশের বকুল গাছ থেকে যে ফুলগুলি ঝরে পড়ার পরও গভীর সুগন্ধ ধরে থাকত তাদের বুকে, সেই ফুল অঞ্জলি ভরে মূর্তির পায়ে দিয়ে আসতাম। ওই কবিতার পঙ্ক্তি দু’টি একবার করে পড়ে নিতাম। আমাদের বাড়িতে সঞ্চয়িতা বইতে যাঁর সই আছে, এখানেও পাথরের থামে তিনি সই করে রেখেছেন জেনে পার্কের সঙ্গে একটা আত্মীয়তার বোধ হত।
পার্কের পরিসীমায় ছিল একটা পিচরাস্তা। যেদিন খেলায় ‘এলেবেলে’ হতাম না, সেদিন ওই রাস্তা ধরে হাঁটতাম, আপন মনে কথা বলতাম, গাছেদেরও নানা প্রশ্ন করতাম। তাদের পাতায় জমা ধুলো মুছতে মুছতে আমার হাতের আঙুল কালো হয়ে যেত। বাড়িতে মা বুঝতে পারত কিনা জানি না, কারণ ফেরার আগে মালিদের ঘরের কল থেকে হাত-পা ধুয়ে নিতাম।
ঘোর শৈশবে পার্কে একা বেড়ানোর দিনগুলিতে তিনটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল, যা আজও মনে আছে। একবার গরমের দুঃসহ দুপুরে কেন জানি না হঠাৎই পার্কে চলে এসেছিলাম। পার্কটা আমাকে টানত, নির্মম মায়ায়। জনমানব নেই কোত্থাও। ধূ ধূ রোদ। একজন লোক আমাকে কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করল, এখানে কী করছ খুকি? বাড়িতে বলে এসেছ? আমি যে গাছেদের সঙ্গে বিড়বিড় করে কথা বলছি আর হাঁটছি, ফ্রকের ঝুল দিয়ে ধুলো মাপছি, এটা তার চোখে পড়েছিল। জোর করে আমাকে টেনে বাড়িতে দিয়ে গেল সে, বলে গেল, একটু খেয়াল রাখবেন। একা একা পার্কে ঘুরছিল। আর একদিন, লোকজনে ভরা এক বিকেলে, এক বুড়ো মানুষ, আমাকে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল কোথায়। প্যারালেল বারের ঘেরা জায়গাটায় মাঝে মাঝেই দেখি তাকে। চেক জামা, কমলা লুঙ্গি, অচেনা নয়। ছোটদের সঙ্গে খেলে, কথা বলে। আমি যেন সম্মোহিত, বুঝতে পারছি এ ছেলেধরা, কিন্তু কিছুই করতে পারছি না। পার্কের সামনের বড় রাস্তাটা পার হতে গিয়ে উল্টো দিকের ভিড়ের ধাক্কায় তার মুঠো খুলে আলগা হয়ে গেল, চকিতে আমি উল্টো দিকে দৌড়। পার্কে আর ঢুকিনি, পাছে সে ফিরে আসে। এক ছুটে বাড়িতে। কিন্তু কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল সে আমায়? কাউকে বলতে পারিনি কথাটা, কেবল মাকে বলেছিলাম চলে যাওয়ার আগে।
[the_ad id=”270085″]
পার্কের পিছনেই ছিল আশুতোষ কলেজের বিশাল বাড়ি। দু’য়ের মধ্যে কোনও দেওয়ালেরও আড়াল ছিল না। ওই কলেজেরই ছাত্র ছিল সে, নাম ছিল মৃণাল। সুদর্শন মনে হত তাকে, আমার বালিকা দৃষ্টিতে। অন্য তরুণদের মতো সিনেমার নায়িকাদের আলোচনায় থাকত না। পার্কের পরিসীমা-পথ দিয়ে ঘোরার সময় আমার সঙ্গে তার দেখা হয়ে যেত, কখনো বা সে ডেকে নিত আমাকে। গুনগুন করে এই গানটিই গাইত, ‘এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।’ ফুলমালার ডোরে, বরিয়া লও মোরে, তার গলায় শুনতে শুনতে মন আকুল হত আমার। গাছেদের সঙ্গে আমার কথা বলাকে মৃণাল অদ্ভুত মনে করত না মোটেই। বরং একদিন সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কি প্রকৃতিকে ভালবাসো? সেই প্রথম অন্য কারও মুখে ভালবাসা শব্দটি শুনে আমার বুকের ভিতর কেঁপে উঠেছিল। তার দিকে না তাকিয়ে, মাথা নামিয়ে বলেছিলাম, হ্যাঁ। মৃণাল বলেছিল, ব্যস, তাহলে আর তোমার চিন্তা নেই। কেন চিন্তা নেই, কিসের চিন্তা, কিছুই বলেনি সে। কিন্তু কথাটা রয়ে গেছিল আমার ভিতরে। পরবর্তী জীবনে ছোটনাগপুরের বিশাল শালের জঙ্গল, সুন্দরগড়ের পর্বতশ্রেণি, মহানদীর আদিগন্ত বিস্তার, কানহার মালভূমি থেকে দেখা অপরূপ সূর্যাস্তের সামনে দাঁড়িয়ে যতবার নিজেকে হারাতে বসেছি, আমার মনে পড়ে গেছে, রবীন্দ্রসঙ্গীত-প্রিয় এক তরুণের ভবিষ্যৎবাণী। প্রকৃতিকে ভালবাসো? তাহলে আর তোমার চিন্তা নেই। না, সত্যিই আজ আমি নিশ্চিন্ত মৃণাল।
পরবর্তী পর্ব ১৭ ডিসেম্বর।
কলকাতায় জন্ম, বড় হওয়া। অর্থনীতির পাঠ প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কবিতা দিয়ে লেখক জীবন আরম্ভ। সূচনা শৈশবেই। কবিতার পাশাপাশি গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, ছোটদের জন্য লেখায় অনায়াস সঞ্চরণ। ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার সদস্য ছিলেন সাড়ে তিন দশকেরও বেশি সময়। মহুলডিহার দিন, মহানদী, কলকাতার প্রতিমা শিল্পীরা, ব্রেল, কবিতা সমগ্র , দেশের ভিতর দেশ ইত্যাদি চল্লিশটি বই। ইংরাজি সহ নানা ভারতীয় ভাষায়, জার্মান ও সুইডিশে অনূদিত হয়েছে অনিতা অগ্নিহোত্রীর লেখা। শরৎ পুরস্কার, সাহিত্য পরিষৎ সম্মান, প্রতিভা বসু স্মৃতি পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবন মোহিনী দাসী স্বর্ণপদকে সম্মানিত। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমীর সোমেন চন্দ পুরস্কার ফিরিয়েছেন নন্দীগ্রামে নিরস্ত্র মানুষের হত্যার প্রতিবাদে। ভারতের নানা প্রান্তের প্রান্তিক মানুষের কন্ঠস্বর উন্মোচিত তাঁর লেখায়। ভালোবাসেন গান শুনতে, গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে, প্রকৃতির নানা রূপ একমনে দেখতে।








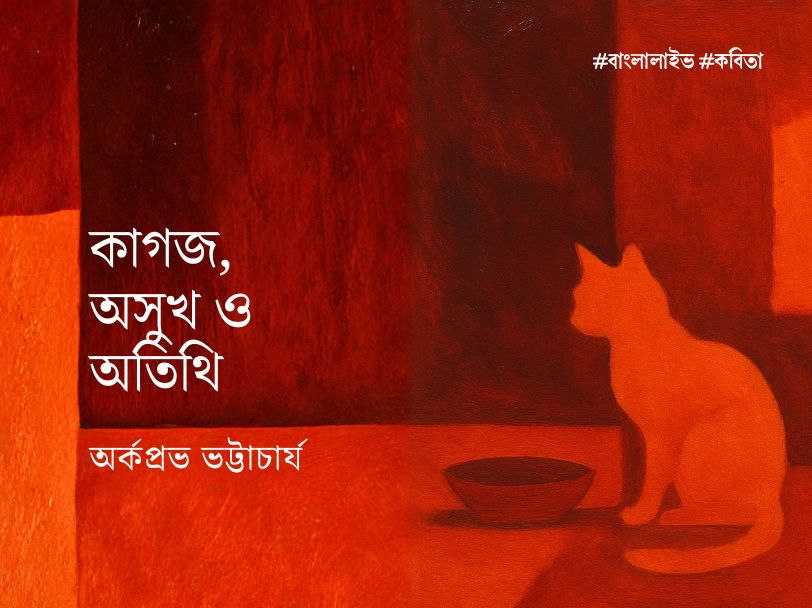


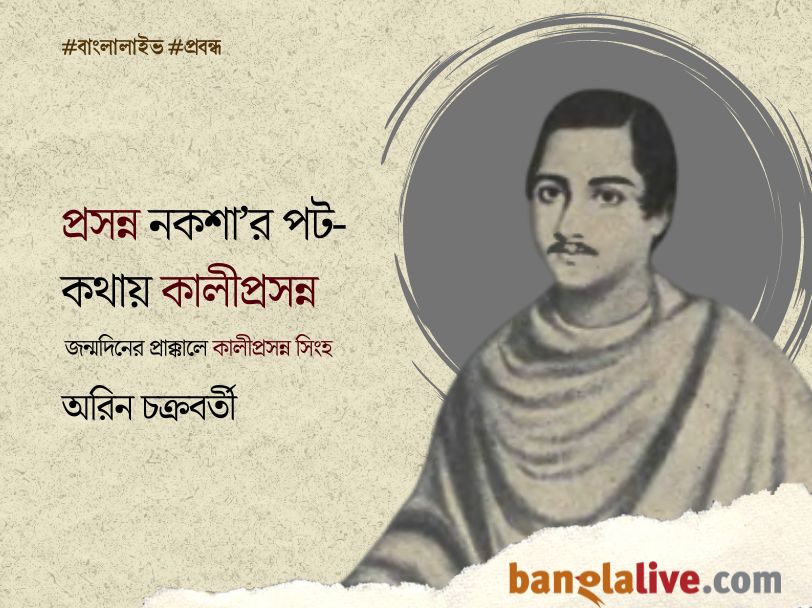




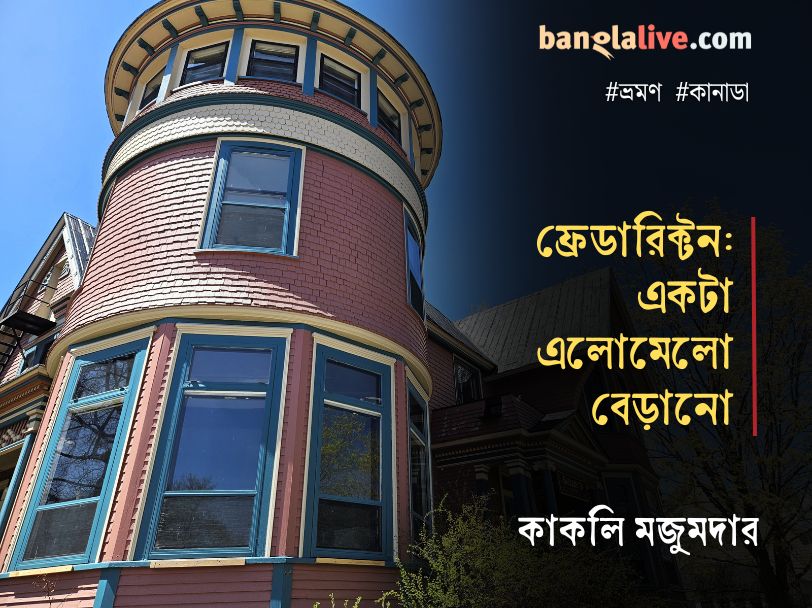
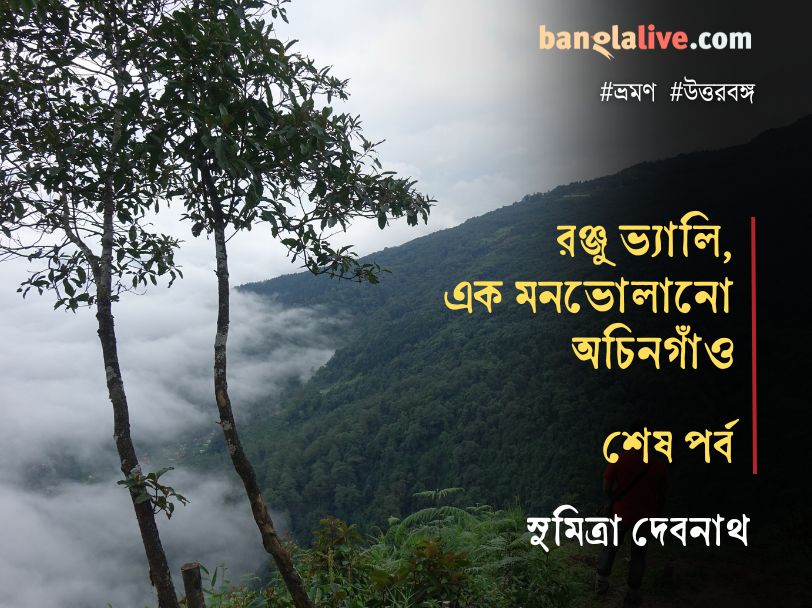








3 Responses
পর্ব ১ এর Link টি খুঁজে পেলাম না।
লেখার শেষে দেওয়া রয়েছে।
জলছবির মতো