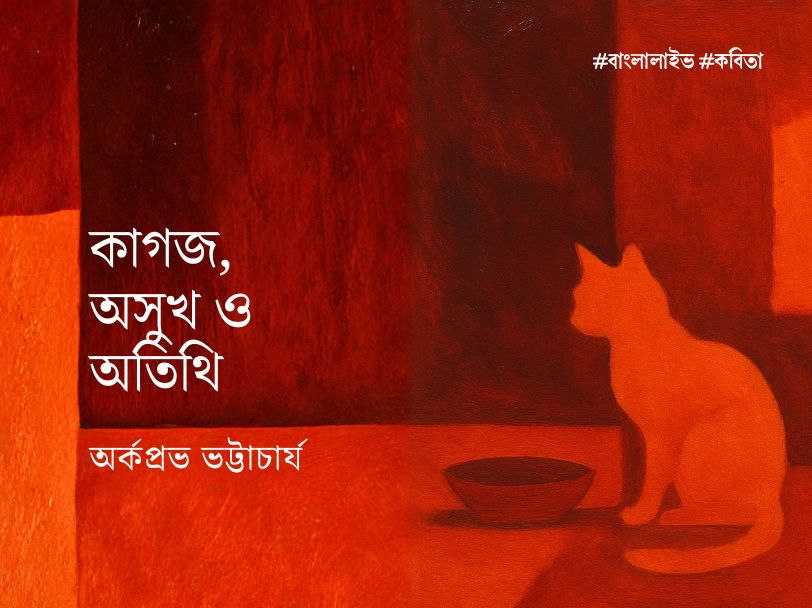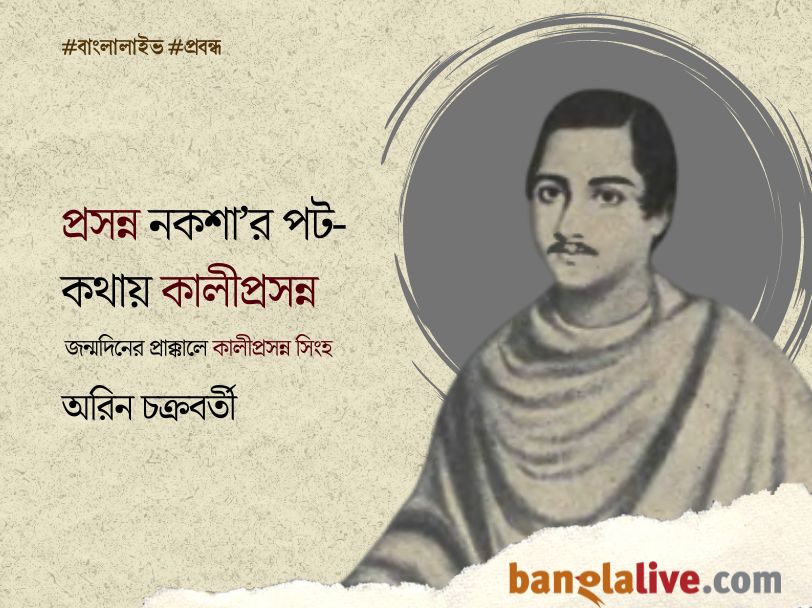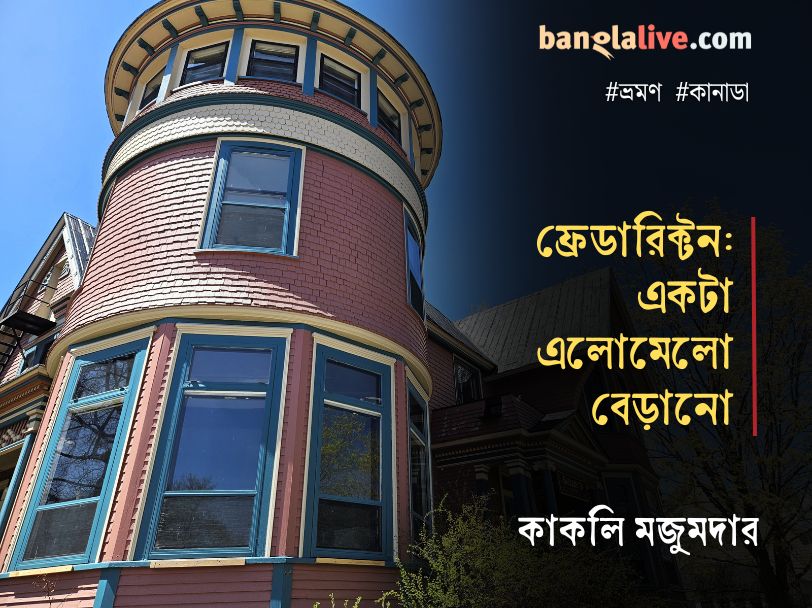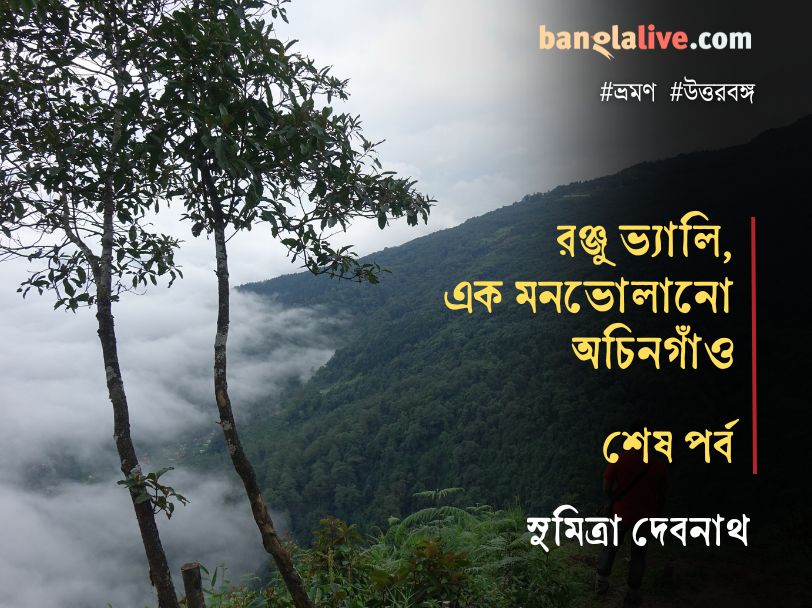ভারতবর্ষের অন্তর্লোক সঙ্গীতে আধারিত। প্রাচীন যুগ থেকে এ দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি যে আধ্যাত্মিক দর্শন থেকে জন্ম নিয়েছিল, তার পথটি ছিল সুরে ভরপুর। ছোট পরিসরে অন্তরজাত দর্শনানুভূতির প্রকাশ-রূপ হল সঙ্গীত। মন ও চিন্তা— দুই-ই স্বস্তি খুঁজে পায়, সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে কোনও কিছু প্রকাশিত হলে। সুর এল কোথা থেকে বা সঙ্গীত আসলে কী বলতে চায়— তার যথার্থ ব্যাখ্যা কোনওদিনই বোধহয় দেওয়া সম্ভব নয়। মানবমনে অজান্তে জেগে ওঠা এ এক অবর্ণনীয় কথন, যা খুঁজে পেয়েছিল ‘সুর’-এর মতো স্বপ্নময় পথ। যুগ যুগ ধরে ভারতে আবির্ভূত সাধক-মহাপুরুষ-মনীষীদের কেউই সঙ্গীতের বাইরে থাকেননি। তাঁদের প্রত্যেকের নিজস্ব কর্মের পথে শক্তির অন্যতম প্রধান উপায় হিসেবে সঙ্গীত এসেছে অবশ্যম্ভাবীভাবে।
ভারতের আধ্যাত্মিক দর্শন এক গভীর জ্ঞানচর্চা ও সাধনার মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে, যার অতলস্পর্শী রূপের সন্ধান আজও হয়ে চলেছে। সারা পৃথিবীর বিখ্যাত দার্শনিক-গবেষকদের কাছে ভারতীয় প্রাচীন দর্শন, এক গভীর অনুসন্ধান ও অনুধাবনের বিষয়, যার কাঠামো সুররসে সিক্ত। আমরা জানি দ্বিতীয়’বেদ’ হিসেবে ধার্য ‘সামবেদ’– পরিপূর্ণ সঙ্গীতে। সারা ভারতে প্রাচীন যুগ থেকে জন্ম নেওয়া সাধক-মহাপুরুষেরা সঙ্গীতে জারিত করেছেন নিজেদের, অঞ্চলভেদে যার রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ পরিবর্তিত হয়েছে। বাংলায় তার নিজস্ব চরিত্র ফুটে উঠেছে শস্যশ্যামলা প্রেমময় প্রকৃতিকে অবলম্বন করে। এই সঙ্গীতপথেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধনরূপের ধারক ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। সাধক হিসেবে এক ব্যতিক্রমী পুরুষরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি। সব সাধকের সাধন-মার্গেরই লক্ষ্য এক পরমসত্যের অনুসন্ধান ও তাতে উপনীত হওয়া। সেই সত্য হল, মানবপ্রেম বা মানুষকে ভালোবাসার এক ঐশ্বরিক জগৎ, যার অন্যতম প্রধান মাধ্যম সঙ্গীত। শ্রীরামকৃষ্ণ এর থেকে আলাদা কিছু ছিলেন না। কিন্তু এই কর্মপথে যে নিজস্ব পদ্ধতিতে তিনি আপনমহিমায় প্রকাশিত হয়েছিলেন, তা ছিল সম্পূর্ণভাবে ব্যতিক্রমী। কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন মাটি থেকে উঠে আসা মানুষ। সারাজীবন থেকেও গেলেন সেভাবেই। চেনা পাণ্ডিত্যের বাগাড়ম্বর জাতীয় কোনওকিছুই তাঁর কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়নি। একবর্ণও কোথাও কিছু লেখেননি। প্রথাগত পড়াশুনার ছাপও পড়েনি জীবনে। শুধু মানুষের সঙ্গে মিশেছেন আর অতি সাধারণ কথায় অনর্গল প্রকাশ করেছেন নিজেকে। আশ্চর্য এখানেই যে, সেই একইরকম কথায় আলোড়িত হয়েছেন প্রাজ্ঞ, পণ্ডিত, উচ্চবর্গীয় থেকে নিরক্ষর নিম্নবর্গীয় মানুষজন পর্যন্ত।
সারা পৃথিবী আজ শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবান্দোলন নিয়ে যে ভাবনাচিন্তা, গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে, তার মূল বিষয়ই হচ্ছে ঠাকুরের দেওয়া অতি সাধারণ কথাধর্মী ‘লোকশিক্ষা’-গুলি। বাক্য বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের যে দর্শনচিন্তার প্রতিফলন ঘটেছিল, তা প্রতি মুহূর্তে সেজে উঠেছে সঙ্গীতে। তবে লক্ষণীয়, সুরের পথে যখনই তিনি কিছু বলতে যা বোঝাতে চেয়েছেন, তা কিন্তু তাঁর কথার মতো সহজ ভঙ্গিতে ঘটেনি। যদি তাঁর সারাজীবনের সঙ্গীত-সরণী দিয়ে আমরা চলতে থাকি, দেখতে পাব কথার মধ্যে অহরহ যেসব গান তাঁর গলায় উঠে এসেছে বা তিনি অন্যের কণ্ঠে শুনছেন যে গানগুলি, তার প্রত্যেকটি গভীর অন্তরদর্শনের বার্তা দিচ্ছে। এখানেই পরিষ্কার, জন্ম থেকেই তাঁর সাধকসত্ত্বার গভীরতা কোন অতলে নিহিত ছিল। বাইরের পড়াশুনা তাঁকে জ্ঞানী করে তোলেনি। সমস্ত কিছুই তাঁর অন্তরস্থ ছিল। এ এক বিস্ময়কর উৎসারণ! বিভিন্ন রচনা ও গবেষণায় দেখা যায়, গান তিনি কারও কাছে প্রথামাফিক শেখেননি। এক অনন্য শ্রুতিধরের ক্ষমতা ধারণ করতেন তিনি। একবার শুনেই গানটি আত্মস্থ হয়ে যেত তাঁর।
আরও পড়ুন: বেপরোয়া গিরিশকে বদলে দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ
এখানেও যা লক্ষণীয়, যেসব গান এসে আশ্রয় নিয়েছে তাঁর অন্তর-আধারে, তার প্রত্যেকটি বিশেষ অর্থবহ হয়ে ধরা দিয়েছে তাঁর কাছে। পাশাপাশি, অন্যদের কাছে যেসব গান শুনতে চেয়েছেন, সেগুলিও চেয়েছেন তিনি অন্তর-দর্শনের সেই একইরকম অবলম্বন হিসেবে। যে কোনও সাধক-মহাপুরুষ, গভীর অন্তর-দর্শনের সাধনায় রত রাখেন নিজেকে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তাই। এই আত্মদর্শনকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তোলার মাধ্যম হিসেবে তিনি বারেবারেই ছুটে গেছেন সঙ্গীতের দ্বারে। উত্তর খুঁজেছেন সুরের দুনিয়ায়। যেখানে তাঁর অনন্ত-অন্বেষণ, স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে সুরের রাস্তা বেয়ে। এভাবেই তা হয়ে উঠেছে মানবজগতকে দেখার শক্তি-সঞ্চয়ের অন্যতম এক নিশ্চিত পথ।
১৮৩৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি (৬ ফাল্গুন ১২৪২ বঙ্গাব্দ) হুগলির কামারপুকুরে পরমহংসদেবের জন্ম। তখন তিনি গদাধর চট্টোপাধ্যায়। সেই তখন থেকে মহাপ্রয়াণের (১৬ আগস্ট ১৮৮৬) কিছুদিন আগে অবধিও তাঁর কণ্ঠে তাৎপর্যপূর্ণভাবে গান উঠে এসেছে। ‘মহাকালী’-রূপে জগন্মাতার সন্ধানে থেকে জগৎজোড়া ‘মা’-কে তিনি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ‘মা’ মানেই স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, আশ্রয়। মানুষকে ভালবাসার মধু হিসেবে ঠাকুর “মা”-কে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন সেই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে– ভক্তি ও প্রেমের মধ্যে দিয়ে। এ কাজে সঙ্গীত যে এক অপরিহার্য উপায় হয়ে উঠবে তা তো বলাই বাহুল্য।
আমরা জানি দ্বিতীয় ‘বেদ’ হিসেবে ধার্য ‘সামবেদ’– পরিপূর্ণ সঙ্গীতে। সারা ভারতে প্রাচীন যুগ থেকে জন্ম নেওয়া সাধক-মহাপুরুষেরা সঙ্গীতে জারিত করেছেন নিজেদের, অঞ্চলভেদে যার রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ পরিবর্তিত হয়েছে। বাংলায় তার নিজস্ব চরিত্র ফুটে উঠেছে শস্যশ্যামলা প্রেমময় প্রকৃতিকে অবলম্বন করে। এই সঙ্গীতপথেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধনরূপের ধারক ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। সাধক হিসেবে এক ব্যতিক্রমী পুরুষরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি।
তাই আমরা দেখি, তাঁর বাল্যকালেই কামারপুকুরে থাকাকালীন, যাত্রাপালায়, লাহা-বাড়ির অতিথিশালায় আসা সাধুসন্তদের ভজনের আসরে, চণ্ডীমণ্ডপের কীর্তন পালাগানের জমায়েতে গদাধর গান গাইছেন। এরপর, কলকাতায় এসে ঝামাপুকুরে দিগম্বর মিত্রের বাড়িতে কিছুদিন কাটিয়ে দাদা রামকুমারের সঙ্গে ১৮৫৬ সালে, উনিশ বছর বয়সে উপস্থিত হলেন রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে।
এ এক অবশ্যম্ভাবী সংযোগ। এই দেবালয় হয়ে উঠল তাঁর সাধনক্ষেত্র। ‘গদাধর’ থেকে তিনি হলেন ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ’। দক্ষিণেশ্বরের সাধনজীবনেই তিনি স্ফুরিত হয়েছিলেন যথার্থরূপে। নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) থেকে শুরু করে তাঁর একেকজন দিকপাল শিষ্যকুলের উত্থান ঘটেছিল এখানেই। এখানে একাধিক গুণীজন সমাবেশ ঘটেছে তাঁর কাছে। তিনিও ছুটে গেছেন অনেকের কাছে। এই দীর্ঘ সাধন-পরিক্রমা ছেয়ে আছে সঙ্গীতে। দক্ষিণেশ্বরে থাকতেই তাঁর গলা কর্কট-রোগে আক্রান্ত হবার পরও তিনি এক মুহূর্তের জন্যেও সঙ্গীতচ্যুত হননি। যত গান তিনি নিজে গেয়েছিলেন সারা জীবনে, তার সংখ্যা ১৮১টি। (‘সঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণ’—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়।)

ভালোভাবে চিকিৎসার জন্য, পরমহংসদেবকে দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয় ১৮৮৫ সালের আগস্টে। প্রথমে বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি কিছুদিন, তারপর বলরাম বসুর বাড়ি হয়ে সেপ্টেম্বরের প্রথমে তাকে আনা হয় ৫৫, শ্যামপুকুর স্ট্রিটের গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের বৈঠকখানা বাড়িতে। এখানে রোগ অত্য অত্যন্ত বেশিরকম বেড়ে ওঠে। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ঠাকুরকে একেবারেই কথা বলতে বারণ করেন। কিন্তু কথা তো বন্ধ থাকেই না, গানও বারেবারেই বেরিয়ে আসে। ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত শ্যামপুকুরের বাড়িতে থাকার পর, ঠাকুরকে নিয়ে আসা হয় ১৪ বিঘে জমির উপর অবস্থিত, পাঁচিলঘেরা, বাগান, পুকুর, গাছপালায় ভরা কাশীপুরের উদ্যানবাটিতে।
এটি ছিল রানি কাত্যায়নীর জামাই গোপালচন্দ্র ঘোষের বাগানবাড়ি। এখানেই পরমহংসদেব তাঁর জীবনের শেষ দশমাস অতিবাহিত করেছিলেন। তথ্য অনুযায়ী যা পাওয়া যায়, এখানেই এক ঐশ্বরিক মুহূর্তে ঠাকুরের কন্ঠে শেষবারের জন্য জেগে উঠেছিল একটি গান। কী গান? আর কেন ও কাকেই বা তিনি শুনিয়েছিলেন সেই গান। এবার আসা যাক সেই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনায়।
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্ত্রী সারদাদেবী ছিলেন তাঁর গানের শেষ শ্রোতা। এক বিশেষ প্রবাহ চলেছিল এই গানের মধ্যে দিয়ে– ঠাকুরের দিক থেকে মা সারদার দিকে। তখন ঠাকুরের অবস্থা খুবই খারাপ। কণ্ঠ প্রায় অবরুদ্ধ। অথচ স্ত্রীকে ভবিষ্যতের পথ চেনানোর জন্য তিনি গানকে অনায়াসে গলায় নিয়ে এসেছেন। ঠাকুর অনেকদিন থেকেই স্ত্রী সারদাকে এক অন্য সত্তায় উত্তরিত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। ‘ফলহারিণী কালীপূজা’-র দিনে ঠাকুর যে তাঁর স্ত্রীকে জননীরূপে আরাধনা করেছিলেন, সে কথা তো সর্বজনবিদিত। তিনি সারদাদেবীকে মাতৃরূপে জীবের আশ্রয়দাত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন, যিনি জগতের ‘মা’ হয়ে উঠলেন।

কাশীপুরে থাকার সময়েই ঠাকুর বিশেষভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন সারদামণির মধ্যে জননীরূপী ঐশীশক্তিকে জাগরিত করার এক কঠোর সাধনকর্মে। বলতেন, ‘ও হচ্চে সারদা, জ্ঞানদায়িনী। মানুষকে জ্ঞান দিতে এসেছে। ও আমার শক্তি।’ একজন আটপৌরে গ্রাম্য বধূ, যাঁর প্রথাগত পড়াশুনা নেই, তাঁকে জগতের ‘জ্ঞানদায়িনী’ রূপে দেখছেন ঠাকুর। এ ‘জ্ঞান’ তো বাইরে থেকে নিয়মের পথে আহরিত নয়— গভীর চেতনাজাত অনন্ত-জ্ঞান! নানারকম মন্ত্রতন্ত্রের ব্যাখ্যাও করতেন ঠাকুর তাঁর স্ত্রীর কাছে। কাগজে এঁকে বোঝাতেন ‘কুলকুণ্ডলিনী’, ‘ষটচক্র’ প্রভৃতি। শেষে একদিন গাইলেন সেই গান, যা এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, শ্রীরামকৃষ্ণ-কণ্ঠে ‘শেষ গান’। (সঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণ দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়)।
শ্রীমুখোপাধ্যায় এই গানটি সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলছেন, কমলকৃষ্ণ মিত্র লিখিত ‘শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতে সমাধি’ গ্রন্থে গানটির প্রথম লাইন হিসেবে যা উল্লিখিত রয়েছে, তা ঠিক নয়। সেখানে আছে— ‘এসে পড়েছি যে দায়…’। কিন্তু, দিলীপকুমার মুখোপ্যাধায়ের মতে ঠিক লাইনটি হল- ‘এসে ঠেকেছি যে দায়…”। এরপর আরও লিখছেন, এ গানটি কোনও সঙ্গীত-সংকলনে নেই। তাই তাঁর বিস্ময়, এরকম একটি অপ্রচলিত গানও যে শ্রীরামকৃষ্ণের জানা ছিল, তা দেখে। এ ব্যাপারে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন।

এ কথা ঠিকই, যে সময় ঠাকুর গানটি গাইছেন, তখনকার কোনও গানের সংকলন-গ্রন্থে গানটি হয়তো ছিল না। আর থাকলেও, সেই সবের ওপর নির্ভর করে যে ঠাকুর গানটি গাইবেন না, তা তো সর্বৈব সত্যি। শুধু এই গানটি নয়, তাঁর গাওয়া সব গানের ক্ষেত্রেই একথা খাটে। সুতরাং, এ ভাবনা অমূলক। কিন্তু, দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতো একজন বিরাট মাপের সঙ্গীতজ্ঞ যখন এই গানটির সম্পর্কে লেখেন, ‘…সঙ্গীত সংকলন গ্রন্থাদিতেও সন্ধান মেলা কঠিন!’ তখন তা বেশ বিস্ময় জাগায়। কারণ, ১৯০৫ সালে প্রকাশিত দুর্গাদাস লাহিড়ীর ‘বাঙ্গালীর গান’ সংকলনে গানটি সংকলিত রয়েছে। সেখানে গানটির শুরুর কথা হিসেবে যা আছে, তা কমলকৃষ্ণ মিত্র ও দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, দু’জনেরই উল্লিখিত বাণী থেকে আলাদা। এসব বিষয় সরিয়ে রেখে, এবার সেই গানটির প্রসঙ্গে যাওয়া যাক।
আগেই বলা হয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর অন্তিম সময়ে কীভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সারদাদেবীকে। এই কর্মপথে এরকম একটি গান যে শেষবারের মতো তাঁর কণ্ঠ থেকে উঠে এসে প্রবেশ করল সারদা-সত্তায়, সে ব্যাপারে কিছু ভাবনা মনে আসে। ওইরকম রোগজর্জর অবস্থায়, যখন কণ্ঠ প্রায় সম্পূর্ণই স্তব্ধ— তখন এই অসামান্য সঙ্গীত-নির্ধারণ যে ঠাকুরের মনে জেগে উঠেছিল, তার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে? গানটির প্রেক্ষিত ও সম্পূর্ণ বয়ানটি উল্লেখ করার আগে সেই অনুমানের পথে হাঁটা যাক।
গানটি গোবিন্দ অধিকারীর রচনা। ইনি ছিলেন প্রাচীন বাংলার এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। পরমবৈষ্ণব। রাধাকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ প্রেমে পাগল এক অনবদ্য পালাগান-রচয়িতা। গানটি বৈষ্ণবমতে গৌরাঙ্গরূপের এক দার্শনিক ব্যাখ্যার ওপর নির্ভরশীল, যেখানে বলা হয়, রাধাকৃষ্ণ-যুগলরূপ, পরজন্মে একদেহে’ গৌরাঙ্গ’ হল। কৃষ্ণপ্রেমে আবির্ভূত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গায়ের বর্ণ হল রাধার মতো গৌর। ‘ভক্তি’ ও ‘প্রেম’— ‘যুগল’ থেকে ‘এক’ হয়ে অন্য এক পূর্ণতার সন্ধান পেল। সেই শক্তি থেকেই অহিংসার পথে জগতে চৈতন্য-বিপ্লব ঘটেছিল।

যে গান থেকে এরকম দর্শন প্রতিভাত হচ্ছে, সেই গানকে ঠাকুর কণ্ঠে ধারণ করছেন তাঁর স্ত্রীকে দেওয়া এক শাশ্বত-শিক্ষার অবলম্বন হিসেবে। এটাই তো ঘটার কথা। কারণ, একথা তো সত্যি যে, রামকৃষ্ণের তিরোধানের পর, যা প্রকাশিত হল ‘মা সারদা’র মধ্যে দিয়ে, তা তো একদেহে রামকৃষ্ণ-সারদা সত্তারই প্রকাশ। সারাজীবন ঠাকুর ভক্তি ও প্রেমের পথে জগতকে চালিত করে গেলেন। যখন নিজে রইলেন না পার্থিব দেহে, স্ত্রীকে সৃষ্টি করে খেলেন জগজ্জননী রূপে। তাঁর সমস্ত অন্তর্দর্শন, স্ত্রী সারদার মধ্যে সঞ্চারিত করে নিজে লীন হয়ে গেলেন তাঁর সত্তায়। ‘সারদামণি’ হয়ে উঠলেন— ‘মা সারদা।’ ‘জননী-সারদা’-কে সৃষ্টি করে, সেই ভক্তিময় ভালোবাসাকে পূর্ণতা দিয়ে গেলেন ঠাকুর। ‘শ্রীমা’ হলেন নারীশক্তি। ‘জননী’-র রূপ তো ‘নারী’-তেই সার্থক ও পূর্ণ। এভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ অন্য এক রূপধারণ করে, নিজ কর্মধারাকে জাগিয়ে রাখলেন ‘সারদা’-রূপে। এই দর্শনবার্তা দেবার লক্ষ্যেই হয়তো স্ত্রীর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণদের শেষবারের জন্য তাঁর সঙ্গীত কণ্ঠকে প্রকাশ করেছিলেন— নির্ধারণ করেছিলেন গোবিন্দ অধিকারীর এই অপূর্ব পদ। শেষে উল্লিখিত হল, সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমার মধ্যে কথোপকথনের ঘটনা এবং গানটির সম্পূর্ণ বাণী। যা থেকে হয়তো এতক্ষণ বর্ণিত ভাবনার কিছুটা নিদর্শন মেলে।
কাশীপুর উদ্যানবাটিতে রামকৃষ্ণ রোগশয্যায় শুয়ে রয়েছেন। তাঁর জন্য রোগপথ্য তৈরি করে, সেই খাবারের বাটিটি নিয়ে শয্যার পাশে বসে রয়েছেন সারদামণি। ঘরে আর কেউ নেই। সব চুপচাপ। হঠাৎ ঠাকুর আকুল হয়ে স্ত্রীকে বলে উঠলেন, ‘দ্যাখো, কলকাতায় লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে। তুমি তাদের একটু দেখো।’ অবাক ও লজ্জাবনত হয়ে সারদাদেবী বললেন, ‘আমি মেয়েমানুষ। আমার পক্ষে তা কি করে সম্ভব?’ এবার পরমহংসদেব নিজের দেহটি দেখিয়ে তাঁর স্ত্রীকে বললেন, ‘এ আর কী করেছে? তোমায় এর চাইতে অনেক বেশি করতে হবে।’ সারদামণির মনে হল, কথায় কথা বাড়ে। তাঁর স্বামীর যা শরীরের অবস্থা, উত্তেজনা ক্ষতিকর হতে পারে। তাই তিনি প্রসঙ্গটিকে চাপা দেবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন— ‘সে যখন হবে, তখন হবে। তুমি এখন পথ্যিটা খেয়ে নাও তো।’ এরকম অবস্থায় ঠাকুর গেয়ে উঠলেন সেই গান। গানটি ঝিঁঝিট রাগে ঢিমে তেতালায় নিবন্ধ। যার সম্পূর্ণ বাণীটি এইরকম–
এসেছি ঠেকেছি যে দায়, কারে কর দায়।
যার দায় সেই তো জানে, পর কি জানে
পরের দায়
মরে দায়ে কতবার রূপ ধরি,
কখন পুরুষ হই সই কখন হই নারী,
হয়ে বিদেশিনী নারী, লাজে মুখ দেখাতে নারি,
কথা বলতে নারি কইতে নারি
নারী হওয়া বিষম দায়।
যার দায়ে কতবার কত রূপ ধরি,
জহরিণী নাপতিনী হয়ে চরণ ধরি,
রাখবো না আর কাল অঙ্গ, স্বরূপে মিশাব অঙ্গ
হবে গৌরাঙ্গ বর্ণ দেখাইব দাও বিদায়।
গানটি গেয়েই পরমহংস তাঁর স্ত্রীকে বলে উঠেছিলেন, ‘ওগো, শুধু কি আমারই দায়? তোমারও যে দায়।’ এরপর বোধহয় আর কিছু বলার দরকার হয় না।
*লেখাটি মাতৃশক্তি কল্পতরু (ডিসেম্বর ২০১৭ – জানুয়ারি ২০১৮) সংখ্যায় প্রকাশিত। পরিমার্জিত রূপে বাংলালাইভে প্রকাশিত হল।
*ছবি সৌজন্য: Wikipedia, Abp, Quora
জন্ম ১৯৬৫-তে কলকাতায়। বেড়ে ওঠা চন্দননগরে। স্কুল জীবন সেখানেই। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক। ছোটো থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। গান শেখাও খুব ছোটো থেকেই। তালিম নিয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। দীর্ঘদিন মার্কেটিং পেশায় যুক্ত থাকার পর, গত বারো বছর ধরে পুরোপুরি লেখালেখি, সম্পাদনার কাজে যুক্ত। পুরনো বাংলা গান, সিনেমা, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়-সহ বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তমকুমারের "হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আনন্দধারা", রবি ঘোষের "আপনমনে", মতি নন্দীর "খেলা সংগ্রহ"। লিখেছেন "সংগীতময় সুভাষচন্দ্র" বইটি। সাত বছর কাজ করেছেন "মাতৃশক্তি" ও "জাগ্রত বিবেক" পত্রিকায়। বর্তমানে নিজস্ব লেখালিখি ও সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত।