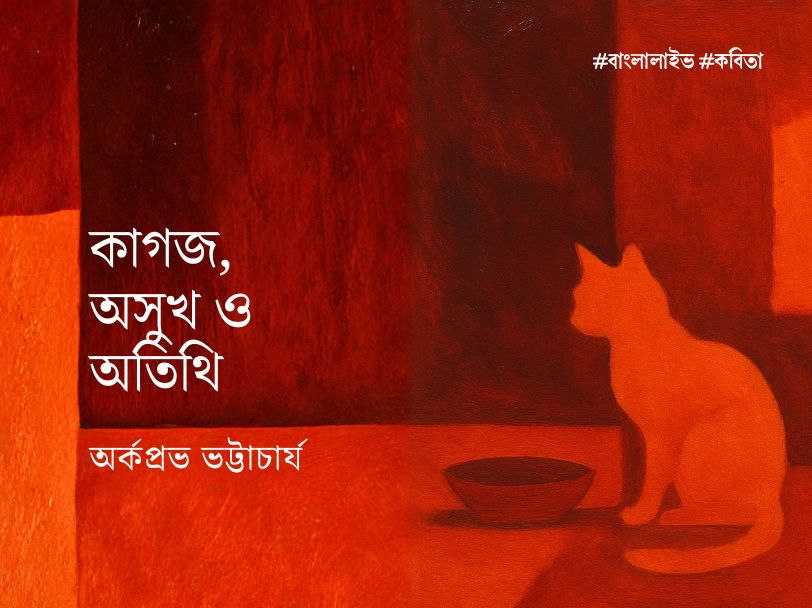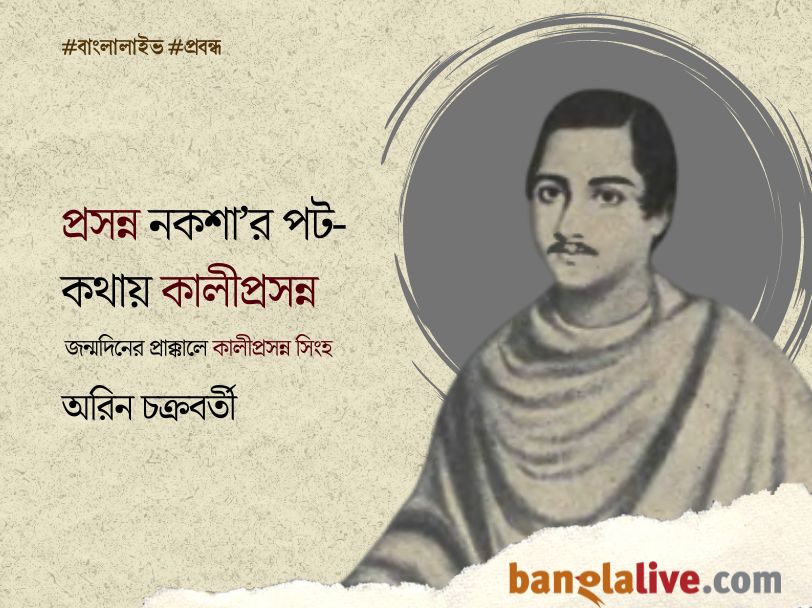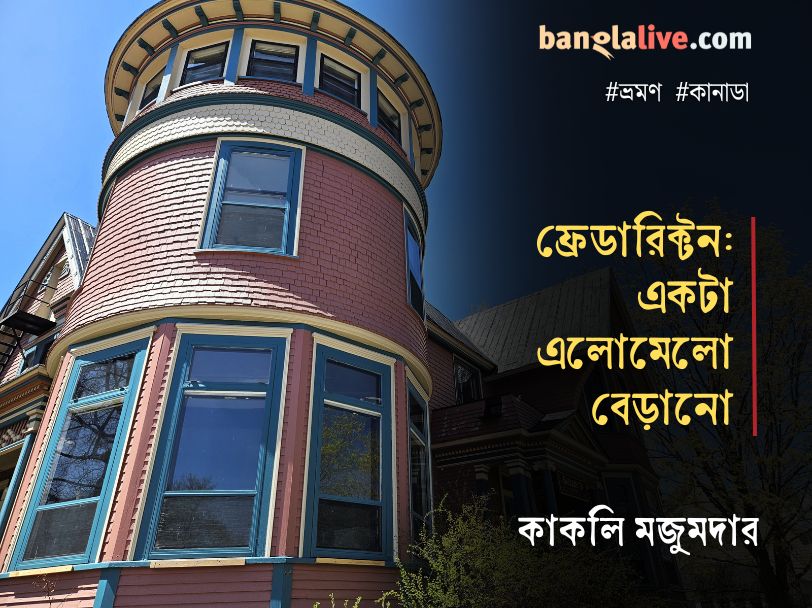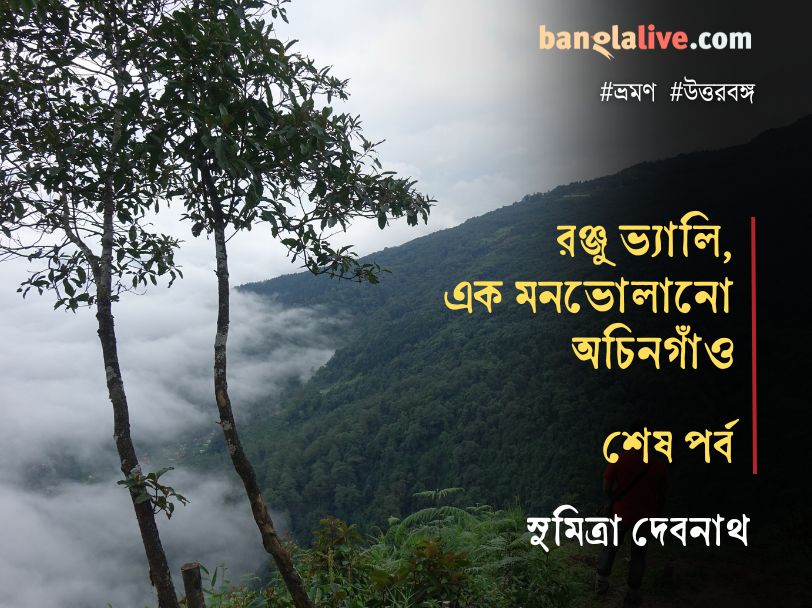আমি তখন ক্লাস টেন। সংসারের শান্ত নদীতে ঢেউ উঠল। বাবার বদলির আদেশ এল। যেতে হবে রৌরকেলা। স্টিল প্ল্যান্ট-এর অডিটের দায়িত্ব। বাবার কাজটা যে বদলির সম্ভাবনাযুক্ত, সেটা আমরা যেন ভুলেই গিয়েছিলাম। এর আগে একবার পদোন্নতি ও বদলির প্যাকেজ একসঙ্গে হাতে এসেছিল। ছেলেমেয়ের পড়াশুনোর দায়িত্বের অজুহাতে বাবা সেটা এত নিঃশব্দে ফিরিয়েছিলেন, তা আমি অন্তত টের পাইনি। এবার তো যেতে হবে। উৎকণ্ঠা। একজনের আয়ে দু’জায়গায় সংসার চালানো। তার উপর দু’জন ডাক্তারি পড়ছে। আমার ক্লাস ইলেভেন হবে পরের বছর। তার উপর কেউ কাউকে কোনওদিন ছেড়ে থাকিনি। ঠিক হয়েছে, মা থাকবেন আমাদের নিয়ে কলকাতার বাসায়। বাবা ওখানে থাকবেন একা। মনখারাপ, তবু মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি?
কিন্তু আরও একটা অপ্রত্যাশিত ঢেউ এল বাবা যাওয়ার সপ্তাহখানেক আগে। মায়ের কান্না, মনখারাপ ইত্যাদির মাত্রা বাড়ছিল। একদিন ছোড়দা আমাকে চুপিচুপি ছোট ঘরে ডেকে নিয়ে বলল, যত সমস্যা তোমাকে নিয়ে। আমি? আমি কী করলাম? তুমি হস্টেলে চলে যাও। নিজেই মাকে বল। আমি আর দাদা দু’জন এখানে থাকব। মা বাবার সঙ্গে রৌরকেলা যাবে। মায়ের জন্য ত্যাগ স্বীকারে সর্বদা প্রস্তুত আমি খাটের তলা থেকে টিনের বাক্স টেনে বার করলাম ছোড়দার সাহায্য নিয়ে। মায়ের মুখে হাসি ফুটল। কিন্তু আমার মনের একটা দিক ভয়ে অসাড় হয়ে গেল।
বাবার একা থাকা নিয়ে মায়ের মনে আশঙ্কা। এবং তা একা পুরুষের যত্নের অভাব সংক্রান্ত নয়। বাবাকে মা চোখের আড়াল করতেন না। পাছে মনোযোগের ঘাটতি হয়, তাই বাবাও পুরো সময় সংসারেই দিতেন। অফিসে, বাজারে, পাড়ায় তাঁর কোনও বন্ধু ছিল না। বদলির আদেশ বাবার রুদ্ধজীবনে কোনও মুক্তির সমাচার বয়ে নিয়ে এসেছিল কিনা, আমার জানা নেই। আমি হস্টেলে স্বেচ্ছা নির্বাসনে যেতে রাজি হওয়ায় বাবা হাসিমুখেই স্কুলে গিয়ে টাকাপয়সা জমা করে এলেন। আমি সঙ্গে গিয়ে নিজের থাকার জায়গা দেখে এলাম। কিন্তু বুক ভেঙে গেল।
মনে হল, আমাকে নিজের ঘরের কোণটুকু ছাড়তে হত না, যদি মা একটু বেশি মা আর কম স্ত্রী হতেন। তবু, আরও এক নিরুপায় যুক্তি দিয়ে বললাম, মা যান না, বাবার সঙ্গে। আমি দাদাদের সঙ্গে থাকি। কিশোরী কন্যার এই অবাস্তব প্রস্তাবে কান দেওয়ার পাত্রী নন আমার মা। তবে এ সবই অবধারিত। ছেলেমেয়ের জন্য যাই করা হোক তারা অতি অকৃতজ্ঞ। পেরেন্টিংয়ের চেয়ে ‘ধন্যবাদ-বিহীন’ বিদঘুটে কাজ আর একটিও নেই। এটা আমিও নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করেছি।
স্কুলের হস্টেল। যেন জনবহুল সভ্যতার মাঝখানে একটি কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। পুরোই জনশ্রুতি ও গুজবের ভিত্তিতে তৈরি ধারণা। ডানদিকের বিকট লম্বা, সারি সারি থামের উপর দাঁড় করানো যে বাড়িটার দোতলায় ইলেভেনের ক্লাস হত, যার দেড়তলায় আমাদের সুন্দর অর্ধবৃত্তাকার লাইব্রেরি, তার তিনতলা পুরোটা জুড়ে হস্টেল। দোতলায় তিনটে স্টাডি রুম আছে। দিনে ক্লাস হয়। রাতে হোস্টেলের মেয়েরা পড়াশুনো করতে পারে।
হস্টেলে কারা থাকে? আমাদের ধারণা, বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানোর দল, যাদের বাড়িতে রাখা যায় না। অথবা অনাথ মেয়েরা, যাদের দেখার কেউ নেই। মোট কথা পড়াশুনোর কোনও পরিবেশ নেই ওখানে। হস্টেলের মেয়েদের রেজাল্ট সবচেয়ে খারাপ হয়, কে না জানে! প্রতি ক্লাসে দু’একজন হস্টেলের মেয়ে আছে, পড়া না পারলে তাদের বরাতে জোটে খোঁটা, এ তো আমরা দেখছি। আমরা যখন স্কুলের ক্লাস শেষ করে বাড়ি যাই, আমাদের পিছনে স্কুলের মস্ত সবুজ দরজাটা বন্ধ হয়ে যায়, মনে হয় হস্টেলের মেয়েরা সব ভিতরে রয়ে গেল। ওদের কী কষ্ট। কোথাও যাবার নেই।

বিকেলের দিকে হস্টেলের রান্নাঘর থেকে দালদায় আটার লুচি ভাজার গন্ধ আসে। সেকেন্ডারি বিল্ডিংয়ের একতলার কোণায় রান্নাঘরটা। তেল কালি পড়া। সারি সারি লো আর হাই বেঞ্চ বসানো। ওখানে বসে বোর্ডাররা খায়। পিছনের একটা খিড়কি উঠোন দিয়ে ঢোকা যায়। আমরা অবশ্য ক্লাসে যাই সামনের সিঁড়ি দিয়েই। হস্টেলের খাবার মুখে তোলা যায় না, মেয়েরা নিজমুখেই বলে। কয়েক মাস আগে চিকেন পক্সে ভুগে উঠেছি। বেশ ভয়াবহ ধরনের সংক্রমণ হয়েছিল। সারা শরীরে কোনও জায়গা ছিল না যেখানে গুটি হয়নি। চোখের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসত লম্বা রক্তের ফিতে। হাত আয়নায় নিজেকে দেখে আর চিনতে পারি না। রোগা থেকে চেহারাটা নেমে গেছে হাড়সর্বস্বতায়। জামাকাপড় ঢলঢল করছে গায়ে।
এই অবস্থায় বাড়ির ভাত ছেড়ে হস্টেল যাত্রার আশঙ্কা, পড়াশুনো করতে না পারার ভয় মনকে আকুল করে তুলল। রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন, ‘অল্প লইয়া থাকি তাই, মোর যাহা যায় তাহা যায়—’ নইলে টোকিও অলিম্পিকে খেলতে যাওয়া ভারতের মহিলা হকি টিমের ক্যাপটেনের জীবনযুদ্ধের কাছে এসব কোন চ্যালেঞ্জই নয়। তবে চোখের সামনে ছোট্ট পরিবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেতে দেখার অনুভূতি চোদ্দো বছরের কারওই সইবে না।
হস্টেল পৌঁছলাম এক মনকেমন করা বিকেলে, কালো টিনের বাক্স ও বেডিং নিয়ে। যেখানে আমার থাকার জায়গা হল, সেটি একটি সুবৃহৎ ডর্মিটরি। বিশাল উঁচু ছাদ, লম্বা চওড়া হলের মধ্যে খান কুড়ি তক্তপোষ। এই রকম দু’টি হলঘর পাশাপাশি। কিন্তু প্রথমটিতে থাকেন হস্টেল মেট্রন। তাঁর জন্য একটি পার্টিশন ঘেরা, প্লাইয়ের দরজা দেওয়া ঘর। ঘরের কাছাকাছি একটি পিলারের পাশে আমার তক্তপোষ। ভাল মেয়ে, ফার্স্ট গার্ল। তাই বিশেষ তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা। পড়াশোনার জন্য নীচের স্টাডি রুমে না গিয়ে খাটে বসে পড়াই ঠিক করলাম। খাটের পাশে একটি ছোট টেবিলে বইপত্র ও বাড়ি থেকে আনা খাবার রাখার ব্যবস্থা। নীচে সেই কৃষ্ণবর্ণ ট্রাঙ্ক। জীবনযাপনের সাদামাটা আয়োজন।
পড়তে কোনওদিনই আমার বেশি সময় লাগে না। সেটা চিন্তার বিষয় নয়। আমার সঙ্গে বিনা কারণে গল্প করে কেউ যেন সময় নষ্ট না করে, সেদিকে মেট্রনের কড়া নজর। সমস্যা হল, ব্যবহারযোগ্য খালি বাথরুম খুঁজে পাওয়া আর স্কুলের সময়ের আগে স্নান করে তৈরি হওয়া। ক্লাস নাইন থেকে শাড়ি পরতে হয়। নীল শাড়ি, রঙিন একরঙা পাড়। সেটিও কেচে ভাঁজ করে হাতের কাছে রাখা। দেরি হওয়া চলবে না, কারণ প্রেয়ারের সময় গানের লিডে আবার আমি। মেট্রনের অনুশাসন আর বড়দিদিমণির প্রত্যাশা– দুয়ের মাঝে চিঁড়ে চ্যাপটা আমি এক নিরীহ প্রাণী। খুঁজে পেতে একতলায় একটা স্নানের জায়গা পেলাম। সেটা কোনও পরিত্যক্ত ঘর, ভিতরে একটা টিউবওয়েল, ভীতিজনক অন্ধকার। কিন্তু এত মশা, মনে হল নিজের হাত দেখতে পাচ্ছি না। বোর্ডাররা কেউ যায় না। তাই লক্ষ লক্ষ মশার কামড় খেয়েও ওটাকে আমি স্নানের জায়গা বানিয়ে ফেললাম।

মেট্রনের কাজটি ঈর্ষাজনক ছিল না। এতগুলি মেয়ের সস্তায় থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে নাজেহাল তিনি প্রায়ই শৃঙ্খলারক্ষায় নতুন নীতি বানাতেন। তা মেয়েদের পছন্দ হত না। একবার কয়েকজন লোকাল গার্জেনকে কোনও কারণে ফেরত পাঠালেন, বোর্ডারদের জানতে দেওয়া হল না। সবাই রেগে ঠিক করল, খাওয়ার ঘরে বিদ্রোহ হবে। না খেয়ে নয়, বেশি করে খেয়ে। যাতে খাবার ফুরিয়ে যায়, এবং রান্নাঘরের কর্মী, স্কুলবাসের ড্রাইভার, এদের জন্য কিছু পড়ে না থাকে। আমাকে বিদ্রোহী গোষ্ঠী কীভাবে করায়ত্ত করেছিল জানি না। তাদের প্রভাবে ছ’টা করে মোটা আটার রুটি খেয়ে আমি পেটব্যথায় ভুগলাম। কিন্তু দমলাম না। স্ট্রাইক বহাল থাকল। মেট্রন জানতেন বিদ্রোহ দমনের অস্ত্র কোথায়। বড়দিদিমণির কাছে নালিশ গেল আমার নামে। যেন আমিই যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি। বড়দিদি মাথায় হাত বুলিয়ে হেসে বললেন, হ্যাঁরে তুই কি ছ’টা রুটি চিরকাল খাস না আজকাল খাচ্ছিস? অমনি আমার চোখে শ্রাবণের ধারা।
ধীরে ধীরে সবই অভ্যেস হয়ে গেল। পড়তি বাজারের কুচোচিংড়ির ঝাল, আটার লুচি, লাল লাল মোটা চালের ভাত, জলের ভাগ সতত বেশি, এমন ডাল। এবং খাবার ঘরে মেয়েদের স্ল্যাং ও স্থূল রসিকতা। তবু রবিবারের জন্য পথ চেয়ে থাকতাম। হাজরা রোডের মা-বাবা শূন্য বাড়িতে দাদারা আক্ষরিক অর্থেই হাত পুড়িয়ে রাঁধত, আমাকে যত্ন করে খাওয়াত। বিকেলে ছোড়দা আবার পৌঁছে দিত হস্টেল। মাঝে মাঝে সদানন্দ রোডে ন’কাকার বাড়িতে ডাক পড়ত ভালমন্দ খাবার জন্য। যেমন বর্ষাদিনে ইলিশের ঝাল, ভাতে। পরিবেশন করতেন কাকিমা আর তাঁর মা। আমি আর শুভা, আমার খুড়তুতো বোন, পাশাপাশি বসে খেতাম। সে সব ছিল সুখের দিন। আর খুব কবিতা লিখতাম। নীল ইনল্যান্ড লেটারের সব কটি পাতা ভরিয়ে বাবা মাকে চিঠি দিতাম কবিতায়। ডে-স্কলার বন্ধুরা সেসব চিঠি লাল ডাকবাক্সে ফেলে দিত।
কলকাতায় জন্ম, বড় হওয়া। অর্থনীতির পাঠ প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কবিতা দিয়ে লেখক জীবন আরম্ভ। সূচনা শৈশবেই। কবিতার পাশাপাশি গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, ছোটদের জন্য লেখায় অনায়াস সঞ্চরণ। ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার সদস্য ছিলেন সাড়ে তিন দশকেরও বেশি সময়। মহুলডিহার দিন, মহানদী, কলকাতার প্রতিমা শিল্পীরা, ব্রেল, কবিতা সমগ্র , দেশের ভিতর দেশ ইত্যাদি চল্লিশটি বই। ইংরাজি সহ নানা ভারতীয় ভাষায়, জার্মান ও সুইডিশে অনূদিত হয়েছে অনিতা অগ্নিহোত্রীর লেখা। শরৎ পুরস্কার, সাহিত্য পরিষৎ সম্মান, প্রতিভা বসু স্মৃতি পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবন মোহিনী দাসী স্বর্ণপদকে সম্মানিত। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমীর সোমেন চন্দ পুরস্কার ফিরিয়েছেন নন্দীগ্রামে নিরস্ত্র মানুষের হত্যার প্রতিবাদে। ভারতের নানা প্রান্তের প্রান্তিক মানুষের কন্ঠস্বর উন্মোচিত তাঁর লেখায়। ভালোবাসেন গান শুনতে, গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে, প্রকৃতির নানা রূপ একমনে দেখতে।