“এই ফড়িং, জলের ধারে একা যাবি না”
যদু-দার গলা পেল ফড়িং। রোগা বলে সিদ্ধার্থকে সবাই ফড়িং বলেই ডাকে। মা অবশ্য ‘সিধাই’ বলে। ‘ফড়িং’ ডাকে একটু মন খারাপ হয়। এবারে পুজোর সময় অসুর ঠাকুরকে খুব করে মনে মনে বলেছে, ওই রকম শক্তপোক্ত চেহারা দিতে। সবাই এভাবে বলে, মন খারাপ হয়ে যায়।
এইসব মন খারাপের হিজিবিজি ভাবছে, তখন কে যেন পাশ থেকে বলল, “কাকে ডাকছে? তোমাকে না আমাকে?”
সিদ্ধার্থ পাশ ফিরে দেখে কেউ নেই। এবারে দেশ জুড়ে অসুখ হয়েছে। কাউকে কোথাও বেড়াতে যেতে দিচ্ছে না। সিদ্ধার্থ খেলতে যেতেও পারে না। ওদের ফ্ল্যাটের বেডরুম থেকে অনিরুদ্ধদের বারান্দা দেখা যায়। দুই বন্ধুতে ওখান থেকেই কথা বলে। আগের মতো একসঙ্গে নেমে পার্কে যেতে পারে না। পুজোর সময় ঠাকুর দেখতেও যেতে পারবে না। বাবা বলল– “চল তাহলে মামাবাড়িতে ঘুরে আসি। ওখানে গ্রামের মধ্যে এখনও এই সব রোগের বালাই নেই।” তাই তো সিদ্ধার্থরা এই গ্রামে এসেছে। একটা ছোট্ট নদীর পারে পরিপাটি করে সাজানো এই গ্রাম, নাম ধূলোমুঠি।
লম্বা মাঠের পরে নদী। এখন মাঠ থেকে ফসল উঠে গেছে। বেশিরভাগ চষা ক্ষেত, ফাঁকা। মাঝে মাঝে পাটকাঠি গোল করে বেঁধে দাঁড় করানো আছে। সিদ্ধার্থ নদীর পারে না গিয়ে, এই পাটকাঠির গোছার পাশে বসে, যেন শিকার করতে এসে পাহাড়ি গুহার পাশে অপেক্ষা করছে। যদিও গুহার খবর আর কেউ জানে না। নিজে নিজেই পাটকাঠির গোছাগুলোকে কখনও গুহা, কখনও দুর্গ এইসব নানা কিছু ভেবে নেয়। তারপর একটা পাটকাঠিকে তরোয়াল বানিয়ে খেলা করে। কিন্তু আবার কে যেন কথা বলে ওঠে, “বললে না তো, কাকে ডাকল?”
“আহা, আমায় ছাড়া কাকে ডাকবে? এখানে আর কেইবা আছে?”
এবার সিদ্ধার্থ বেশ ঝাঁঝিয়ে উত্তর দেয়। পাশ ফিরে দেখে কেউই নেই। পুজোর পর রোদে একটা দুঃখী চাদর মোড়া থাকে। বিকেলের দিকে একটা অদ্ভুত কুয়াশার স্তর পাটকাঠির খানিক ওপর দিয়ে ভেসে যায়। সিদ্ধার্থ ওইদিকে তাকিয়ে একটু কি ভয় পেল? এই সময় মাঠে কেউ নেই। আর-একটু এগিয়ে নদীর ঘাটও ফাঁকা। কাঁপা গলায় বলে, “কে কথা বলছ?”
“আমি রে আমি। আমার নাম করে ডাকছে, চিনতেই পারছ না?”
এবার সিদ্ধার্থর চমক লাগে। পাটকাঠির গা ঘেঁষে একটা বেশ মোটাসোটা ফড়িং উড়ছে। লেজটা শুকনো লঙ্কার মতো লাল। কথাটা কি এই ফড়িং বলল? ও যেন আন্দাজ করল– “কেন আমরা বুঝি কথা বলতে পারি না? যত কথা শুধু মানুষদের?”
“আমি কী করে জানব? কেউ তো আমার সঙ্গে আগে কথা বলেনি।”
“কী করে কথা বলবে? তোমরা কথা বলতে চাও? শুধু ল্যাজে সুতো বেঁধে ঘোরাবার চিন্তা।”
“আমি কখনও করিনি।”
“আরে তুমি করনি হয়তো, তবে তোমার বয়সি অনেকেই করে। এই ধুলোমুঠি গ্রামে অনেক বিচ্ছু ছেলে আছে।”
“আমি তো এখানে থাকি না। এখানকার কাউকে তেমন চিনিনা।”
“সে খুব ভালো। এদের কে চিনলে আর দেখতে হবে না। সারাক্ষণ বিড়ালের গায়ে জল দিচ্ছে, ব্যাঙের গায়ে ঢিল মারছে, আমাদের ল্যাজে সুতো বাঁধছে, কুকুরের ল্যাজে কালিপটকা, আরও কত কী!”
“না না আমি ও সব করি না। আমার বাজি পোড়াতে ভয় করে।”
“তা তোমায় দেখেই বুঝেছি। একা একা বসে পাটকাঠি চিবোচ্ছ।”
“মোটেও চিবোই নি। একবার দাঁতে লাগিয়ে দেখছিলাম।”
“ওই হল! এখন একটু সরে বসো, নদী থেকে হাঁসের দল আসছে।”
সত্যিই একটু পর হাঁসেদের প্যাঁক প্যাঁক শব্দ শোনা যেতে থাকে। সিদ্ধার্থ অবাক হয়ে বলে– “তুমি কীকরে বুঝলে, যে হাঁস আসছে?”
“আরে তোমাদের মতো নাকি? আমার একেকদিকে বাইশ হাজার চোখ। কত কিছু নজর করতে হয়। না হলে, ওই হাঁস কিংবা ফিঙে আমায় টপাত করে খেয়ে ফেলবে। আমি একটু তফাতে যাই।”
এই বলে ফড়িংটা যেন হন্তদন্ত হয়ে উড়ে গেল। সিদ্ধার্থ তাকিয়ে দেখে প্রায় দশ বারোটা হাঁস নিজেদের গায়ে গায়ে ঠেলাঠেলি করতে করতে নদীর পার থেকে মাঠ ডিঙিয়ে আসছে। ওইদিকে ওদের বাড়ি। দিন শেষ হয়ে আসছে দেখে, ফিরছে। হাঁসগুলো সিদ্ধার্থকে তেমন আমল না দিয়ে এগিয়ে গেল। তখনই আবার সেই লাল লেজের ফড়িংটা বোঁ করে ঘুরে এলো।
“সবাই তো বাসায় ফিরছে, তুমিইবা এখানে ঘট হয়ে বসে আছ কেন? যাও ঘরে যাও।”
“এখানে টিভির কার্টুন চ্যানেল আসে না। ঘরে ফিরে ভালো লাগে না।”
“তোমাদের যত ভুলভাল সমস্যা। আমাদের ওসব বালাই নেই। খাই-দাই উড়ে বেড়াই। আবার আমায় কেউ টপ করে খেয়ে নেয়। ব্যাস গল্প শেষ।”
“এবাবা তোমার ভয় করে না?”
“আরে ছোঃ! ভয় আবার কী? পাঁচ সপ্তাহ কাটিয়ে দিলে এমনিই সাঁই, তার চেয়ে ফিঙের পেট ভরাতে পারলে তো ভালোই হয়।”
“সাঁই, মানে?”
“ও তুমি বুঝবে না। তোমাদের অল্প বয়স।”
“কীসের অল্প বয়স? আমার এখন সাত বছর প্লাস।”
“আমি তো চোদ্দদিন প্লাস। মানে আজ সকালে চোদ্দদিন হল।”
সিদ্ধার্থের হাসি পেল। বলে কী? কোথায় সাত বছর আর কোথায় চোদ্দ দিন? এটা কোনও হিসেব হল? আবার যেন ফড়িংটা টের পেল। বলল– “ফসিল কাকে বলে জানো?”
“হ্যাঁ পড়েছি, চাপা পড়ে পাথর হয়ে যায়।”
ফড়িংটা যেন হাসল, “আমাদের বত্রিশ কোটি বছরের ইতিহাস। পৃথিবী জমিয়ে রেখেছে। তোমরা তো সেদিনের লোক! মেরেকেটে তিন লক্ষ বছর! আর ভেবে ফেলেছ, এই চোদ্দশো কোটি বছরের পৃথিবীটা শুধু তোমাদের?”
এত বড় বড় অঙ্ক শুনে সিদ্ধার্থর গুলিয়ে গেল। হাত পা নেড়ে বলে, “আমার দাদু অনেক পুরনো। নদীর ধারের ওই বটগাছটা ওর লাগানো।”
ফড়িং এবার হেসেই ফেলে, “যাও যাও ঘরে যাও। অন্ধকার নামছে। আমি চলি। কাল এদিকে এলে দেখা হবে।”
বাড়ি ফিরে মায়ের কাছে একচোট বকুনি। “সারাদিন আদাড়ে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ। পুজো শেষ, এবার বই নিয়ে বসো। স্কুল খুললেই পরীক্ষা, তার খেয়াল আছে?”‘
“আমি তো নদীর ধারে যাইনি। ফড়িং-এর সঙ্গে গল্প করছিলাম।”
“ভালো, নিজের সঙ্গে গল্প করা ভালো। এবার হাত পা ধুয়ে এসো।”
সিদ্ধার্থ বুঝল, মা ফড়িং বলতে ওকেই বুঝেছে। আর কথা বাড়ায় না।
রাতে খাবার টেবিলে খেয়াল হয়, বাবার হাতে আংটি নেই। খোঁজ খোঁজ। ঘরের কোথাও পাওয়া গেল না। সকলে বলল, সাঁতার কাটতে গিয়ে হয়তো নদীতে পড়েছে। সকালে যদু-দা কে বলা হবে খুঁজে দেখতে।
খুব ভোরবেলা গরুর দুধ দুইতে আসে যদু-দা। ফ্ল্যাটে সিদ্ধার্থের ঘুম ভাঙতে চায়না, কিন্তু এখানে এলে আলো ফোটামাত্র চোখ খুলে যায়। আর তখন ঘরে থাকতেও ইচ্ছে করে না। একছুটে বাইরে চলে আসে। ঘাসগুলো কেমন ভেজা ভেজা থাকে। নাক টেনে বড় করে শ্বাস নিলে পাঁচমেশালি গাছের পাতার সবুজ গন্ধ নাকে আসে। আর অবাক হয়ে যদু-দাকে দেখে। কেমন করে বাছুরকে নিয়ে আসে, তারপর খানিক খাইয়ে, বালতি ভরে দুধ নেয়।
আজ বাবাও উঠে এসেছে। যদু’দা কে আংটির কথা বলে। শুনে যদু-দা বলে, “তাহলে এখনি নামতি হয়। বেলা বাড়লে জল ঘোলা হইয়ে যাবে।”
দুধের বালতি রান্নাঘরের দাওয়াতে রেখে, নদীর দিকে চলল, সঙ্গে বাবা। সিদ্ধার্থও পিছুপিছু।
বেশ খানিক ডুব দিয়ে এসে যদু কিছুই পেল না। জলের কাছে সিদ্ধার্থর বাবা আর দুয়েকজন মানুষ দাঁড়িয়ে। সিদ্ধার্থ ঘাট থেকে একটু দূরে। তখনই বোঁ করে আওয়াজ। ঠিক ধরেছে। কালকের সেই ফড়িংটা এসেছে। এসেই ভারিক্কি ভঙ্গিতে বলে, “আচ্ছা বোকা তো? নদীর স্রোত বলে একটা ব্যাপার আছে তো? কাল এই ঘাটে হারিয়েছে, তো আজও সেখানেই পাবে? ওকে বল, ওই খুশিনগরের ঘাটে একটা বাবলা গাছ ঝুঁকে আছে, তার নিচে খোঁজ করতে।”
“তুমি কী করে জানলে?”
“আচ্ছা মুশকিল! আমরা জানবো না তো তোমরা জানবে? সেদিনের মানুষ? আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৃথিবীর খবর লেগে আছে। আমরা জলের ভেতর লার্ভা খাই আবার জলের ওপরের পোকাও খাই। তাই সবের খবর থাকে। খেয়াল করে দেখবে, আমাদের ডানাতেই রামধনু লেগে থাকে। যাও আর দেরী কোরো না। আবার ঢেউ লাগলে ফস্কে যাবে।”
ফড়িং-এর পরামর্শ মতো সিদ্ধার্থ ঘাটের কাছে গিয়ে, খুশিনগরের কথা বলে। যদু আর সিদ্ধার্থর বাবাও খানিকটা অবাক হয়ে তাকায়।
ধুলোমুঠির লাগোয়া গ্রাম খুশিনগর। তবে এই ঘাটে লোক চলাচল কম। যেন চুপ করে বাঁশঝাড় মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছে। যদু খুঁজে খুঁজে বাবলা গাছ ধরে জলে নামে। স্নানের ঘাট নেই বলে ওঠানামা কষ্টের। তবে বেশি কষ্ট পেতে হয়না। দুই ডুবেই আংটি নিয়ে উঠে আসে।
বাড়িতে খুশির হাওয়া ওঠে। যদু-দাকে পুরস্কার দেওয়া হয়। সবাই মিলে সিদ্ধার্থকেও খুব সাব্বাশ দেয়। কেমন বুদ্ধিমান ছেলে! মা এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।
এক ফাঁকে সিদ্ধার্থ আবার পাটকাঠির গুহার কাছে আসে। আসল লোককে ধন্যবাদ জানাতে হবে। কিন্তু সেখানে কাউকেই খুঁজে পায় না। গলা নামিয়ে ‘ফড়িং’ বলে দুতিন বার ডাকল। একটা পাটকাঠির ওপর লম্বা লেজের একটা ফিঙে বসেছিল। সেটা যেন একটু ঢেকুর তোলার মতো শব্দ করে উড়ে গেল। হঠাৎ চোখে পড়ে ঘাসের ওপর কী যেন চকচক করছে। তুলে দেখে একটা স্বচ্ছ ডানা। রোদের আলোয় কেমন ঝিকমিক করে ওঠে, সাত রঙা আলো ঠিকরে বেরয়। ঠিক যেন রামধনু!
এক সর্বগ্রাসী হাঁ-করা চোখ নিয়ে, কলকাতা ও সংলগ্ন শহরতলিতে জন্ম ও বেড়ে ওঠা সৌরভের। যা দেখেন, তাই মনে হয় ছুঁয়ে দেখলে ভালো হয়। কিছুটা প্রকৌশল, কিছুটা ছবি আঁকা, ভাষা শিক্ষা, থিয়েটার এমন আরও অনেক কিছু। এভাবেই ভেসে চলা। শৈশবে স্কুল পত্রিকায় হাত পাকিয়ে রেল স্টেশনে দেওয়াল পত্রিকা, লিটল ম্যাগাজিনের পাতা থেকে প্রাতিষ্ঠানিক বাণিজ্যিক পত্রিকায় পৌঁছনো। জীবিকার তাগিদে কম্পিউটারের সাথে সখ্য। পাশাপাশি কয়েক মাইল ‘কোড’লেখা চলে সমান্তরাল। কর্পোরেটের হাত ধরে পৃথিবীর কয়েক প্রান্ত দেখে ফেলার অভিজ্ঞতা। সবই উঠে আসে লেখায়। আপাততঃ কলকাতা ও ঢাকা মিলিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা নয়।




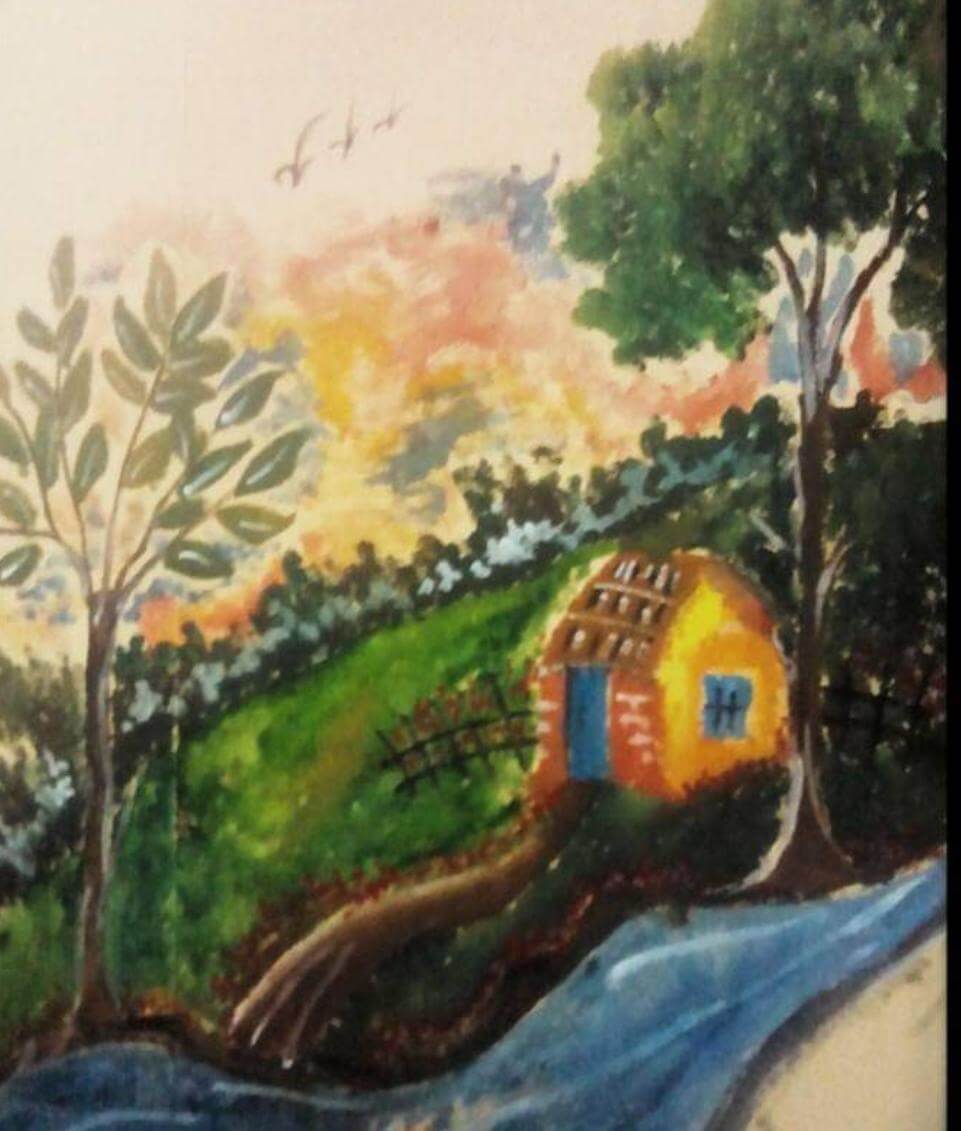



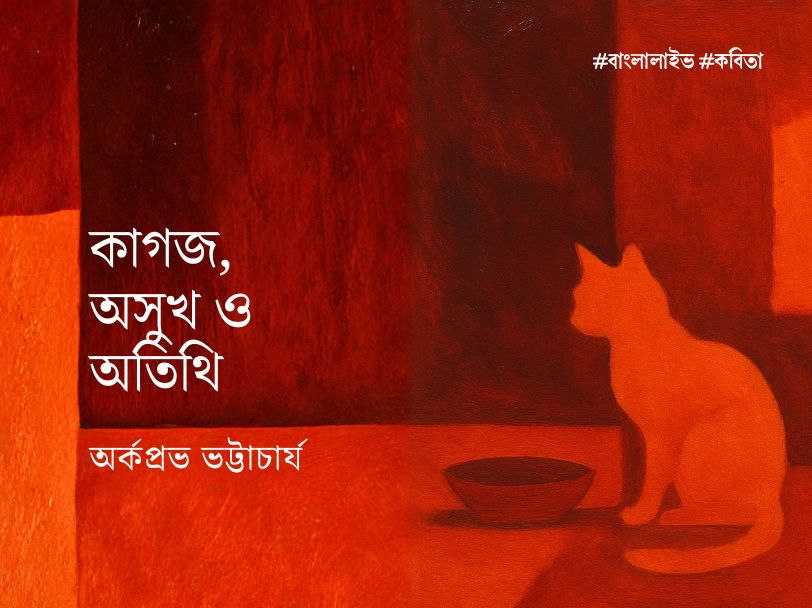


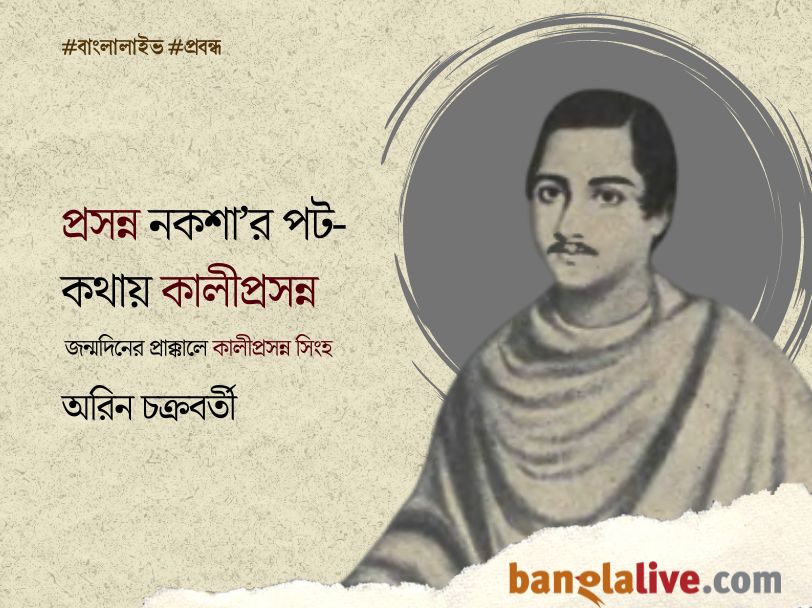




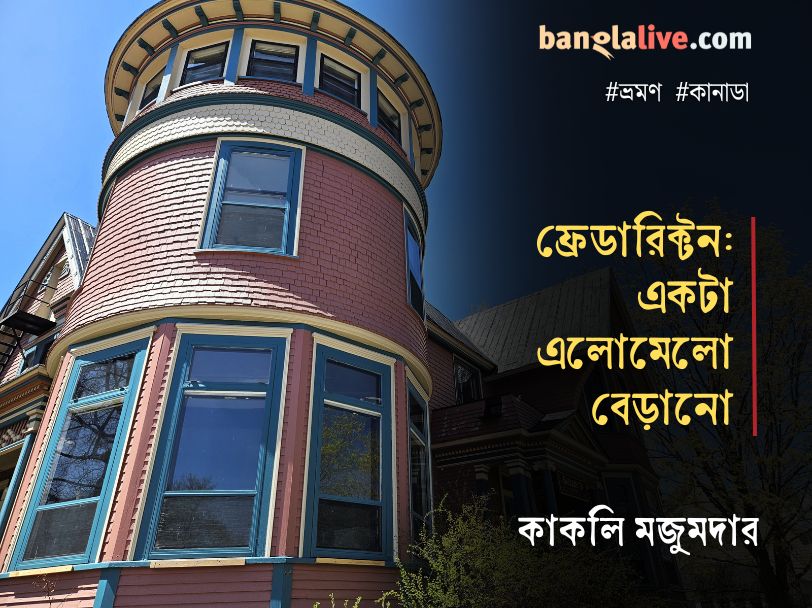
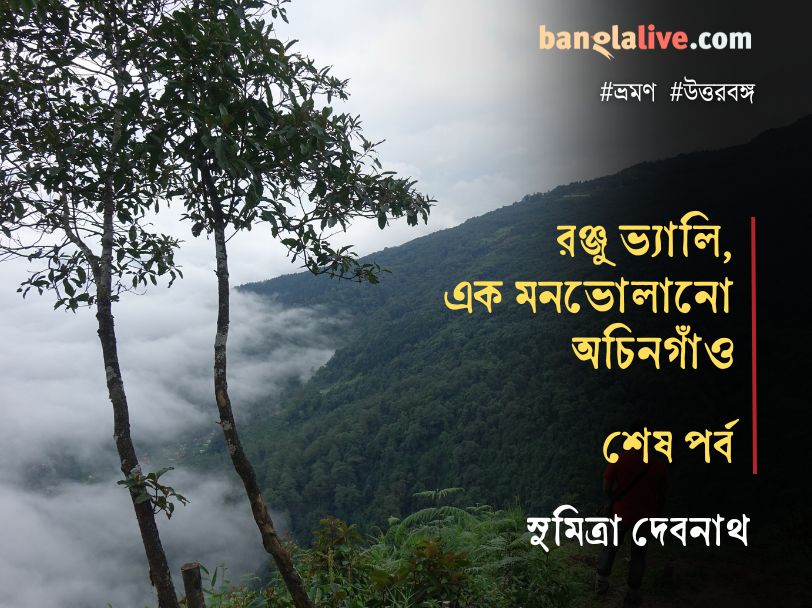








3 Responses
As usual onobodyo 🙏 Sourav Da….
Bhalo laglo Souravda..
মন ভালো হয়ে যায় এত সুন্দর গল্প পড়লে। অসংখ্য ধন্যবাদ এমন একটি গল্পের জন্য।